বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি আর বজ্রকঠিন চরিত্রের কল্পকথাগুলি একটু একটু করে ধুলো হয়ে উবে যাচ্ছে অনেকদিন হল। এখন তর্কটা এসে দাঁড়িয়েছে তিনি আদৌ এদেশের – দেশের মানুষের – জন্য শুভ কিছু, কল্যাণকর কিছু করে – বা অন্তত শুরু করে – যেতে পেরেছিলেন কি? নাকি স্রেফ ব্রিটিশ প্রভুদের ইশারায়, অঙ্গুলিহেলনেই বাঁধা ছিল তাঁর কার্যপরম্পরা? ঘুলিয়ে ওঠা কাদাজল সামান্য স্বচ্ছ করার প্রচেষ্টায় অশোক মুখোপাধ্যায়। এটি ৩’য় পর্ব। ১’ম ও ২’য় পর্ব প্রকাশিত ক্রমান্বয়ে এই লিঙ্কে এবং এই লিঙ্কে।
[৫]
মেকলের সম্পর্কে এদেশের একদল র্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীর খুব উচ্চ ধারণা। তিনি নাকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে যা কিছু শিক্ষা পরিকল্পনা করেছিলেন ভারতীয় “ভদ্রলোক” “রেনেশাঁস-উপজ”গণ হুবহু তাকেই রূপদান করে গেছেন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষার পরিকল্পনাও নাকি মেকলেরই ভাবসম্প্রসারণ। কোম্পানি শাসকরা যেমনটি চেয়েছিল, তিনি তাই করে গেছেন! কিংবা, বিপরীতক্রমে, বিদ্যাসাগর কোম্পানির ইচ্ছাই পূরণ করে গেছেন।
বেশ বেশ। চলুন, আমরা এবার ঋত্বিক ঘটকের পরামর্শ একটু মেনে দেখি।
শুরুতে জানিয়ে রাখি, মেকলে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থে অনেক অনেক কেরানি আর বেশ কিছু জজ, উকিল, দারোগা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের ট্রেনিং দেবার জন্য কিছু শিক্ষকও তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি বাংলা ভাষার উন্নতি চেয়েছিলেন? কিংবা বাংলা সাহিত্যের বিকাশ? তাঁর বিস্তারিত রিপোর্টের কোথাও কোনো প্রস্তাবে আছে নাকি সেরকম কিছু বাণী?
নেই।
অথচ, বিদ্যাসাগর অক্ষয় দত্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাজকর্ম অনুসরণ করলে দেখা যায়, ১৮৬০-এর দশক থেকে বাংলা সাহিত্য, নাটক এবং সংবাদপত্র হু-হু করে বাড়ছে। হ্যাঁ, এ তো ঠিকই যে অধিকাংশ নাটকের বিষয় হচ্ছে পৌরাণিক ও ধর্মীয় উপাখ্যান এবং সংবাদপত্রগুলিতে বেশিরভাগ খবরই হচ্ছে ইংরেজ সাহেব এবং রাজাজমিদারদের বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা। কিন্তু তার মধ্যেই দুচারটে করে বিদ্রোহাত্মক নাটক রচনাও বেরতে শুরু করল কোন যাদুবলে? সংবাদপত্রগুলিতেই বা মাঝে মাঝে শুধু জমিদার সম্প্রদায় নয়, কোম্পানির শাসকদের নিন্দা সমালোচনা মূলক নানা খবর আসতে লাগল কার প্রেরণায়? হরিশ মুখার্জীর Hindu Patriot পত্রিকাই বা অপেক্ষাকৃত গরম ভাব নিয়ে লেখালেখি করে চলেছিল কোন সাহসে? এই সব কী করে হল? মেকলে এটাও চেয়েছিলেন বলে হল, নাকি, অন্য কিছু কলকাঠির ব্যাপার ছিল? “তত্ত্ববোধিনী” পত্রিকায় অক্ষয় কুমার দত্ত কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে বলতে গিয়ে সরকারের জমিদার তোষণ নীতি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও “বঙ্গদর্শন”-এ বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে অত তীব্র না হলেও যথেষ্ট গভীরতা সহ অনেক ভালো ভালো প্রশ্ন তুললেন। মেকলের ফিলটার দিয়ে এগুলো গলে বেরল কীভাবে?
বিপরীত দিকে, সংবাদপত্রগুলোকে আটকানোর জন্য একের পর এক কালা কানুন বানাতে হচ্ছিল কেন? ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট-এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন মুৎসুদ্দি-তাত্ত্বিকরা? ১৮৭৬ সালের আফঘান যুদ্ধের পর বাংলার প্রেসগুলিতে কী এমন ঘটেছিল যে এমন একটা কালা আইন আনতে হল সাদা শাসকদের? মেকলে তাহলে কী শিখিয়ে গেলেন দেশি সাহেবদের? মেকলের কলে যদি কেবলই কিছু বশম্বদ ইংরেজি জানা লেখকপুঞ্জ তৈরি হয়ে গিয়ে থাকেন, যাঁরা মনেপ্রানে কেবল ইংরেজ শাসনের দীর্ঘায়ু কামনা করে বেড়ান, সেই তাঁদেরই লেখনীতে সাহেবদের প্রাণে অত ভয় জাগল কেন? বড়লাট রিপনের উদ্যোগে ইলবার্ট বিল এনেও কেন তাকে সংশোধন করতে হয়েছিল? ভারতে বসবাসকারী সাদা চামড়ার লোকেরা, নিলকর সাহেবরা মেকলে-পুষ্ট দেহে-ভারতীয়-মনে-ইংরেজ বিচারকদের সম্বন্ধে অতটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল কেন রে বাপু?
এই দুই জায়গার মধ্যে কোথাও একটু গোলমাল আছে বলে ঠেকছে না?
যাঁরা সেই মেকলে-সর্বশক্তিমানতায় বিশ্বাস করে এক কালে বাংলার রেনেশাঁসকে অস্বীকার করেছিলেন, রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে যাকেই পেরেছেন ইংরেজদের মুৎসুদ্দি বানিয়ে ছেড়েছিলেন, এবং তাঁদের যাঁরা একালের উত্তরাধিকারী, তাঁরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতদের একাংশের এই ইংরেজ বিরোধী আচরণের ব্যাপারে কিছু সদর্থক ব্যাখ্যা দেবেন বলে নিশ্চয়ই আশা করা যায়। এটা তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।
আর একটা ভালো প্রশ্ন তুলেছেন ফেসবুকে আমার অন্যতম বন্ধু করবী মুখোপাধ্যায় আমার এই চার নম্বর পরিচ্ছেদের প্রেক্ষিতে; সেটাও এক দিক থেকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। মেকলে বিরোধী রবীন্দ্রনাথ কী করে আদ্যন্ত “মেকলে-সৃষ্ট” বিদ্যাসাগরের অত প্রশস্তি করে গেলেন? তাহলে কি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা পদ্ধতির অত বিরোধিতা করেও রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত মেকলে বৃত্তের বাইরে নন? নাকি, তিনি মেকলের সন্তানদের চিনতেই পারলেন না?
আমাকে যদি জিগ্যেস করেন তো বলব, আসলে মেকলে-থিসিসটিই এই রকম অনেক জায়গাতে খাটে না। রবীন্দ্রনাথের সময়ে সমস্তটা কবির পক্ষে হয়ত বোঝা সম্ভব ছিল না। ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার প্রতি কবির বিতৃষ্ণা ছিল — থাকাটাই স্বাভাবিক — আর কবি ভেবেছেন, মেকলে চেয়েছিলেন, ইংরেজ শাসকরাও চেয়েছিল বলেই এমনটা ঘটেছিল। তা তো নয়। যেহেতু আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার আয়োজন হয় একটা অস্বাভাবিক, ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে, এর মধ্যে অনেক রকম সমস্যা ছিল, বিকৃতি ছিল। পাঠ্য বই ছিল সবচাইতে বড় সমস্যা। সেটা মেকলে না এলেও হত বা সেই সময় হতে পারত। কিন্তু বিদ্যাসাগর মেকলের লাইনে চিন্তা করেননি, শিক্ষার পরিকল্পনাও সেই অনুযায়ী করেননি। তিনি দেশের সেই সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেশের সামগ্রিক প্রগতির স্বার্থে যতটা পারা যায় ইংরেজ সরকারের থেকে সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করে গেছেন। কিছুটা পেরেছেন, কিছুটা পারেননি। কিন্তু এই যে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগরকে পছন্দ হল, আর ইংরেজ শাসকরা বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনা মেনে নিতে পারেনি — এই দুইয়ের মধ্যেই রয়েছে বিদ্যাসাগরের কাজের গুরুত্ব বোঝার একটা সহজ শ্রেণিস্বার্থগত চাবিকাঠি।
এখানে অন্য একটা বিষয়কেও বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। আসলে বাংলার রেনেশাঁসের বিরুদ্ধে দুই মেরুপ্রান্ত থেকে একই রকম প্রশ্ন উঠেছে।
ভারতে একদল বুদ্ধিজীবী (বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, তরুণ সান্যাল, ধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এবাদত হোসেন, অশোক সেন, প্রমুখ) ১৯৬৮-উত্তর নকশালপন্থী আন্দোলনের উত্তাল আবেগে মার্ক্সবাদের নাম করে বিচার করতে গিয়ে প্রথমে ইউরোপের রেনেশাঁসের একটা মডেল ভেবে নিয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের যুগে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণি সর্বত্র সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত শোষিত কৃষকদের সমবেত করে কৃষি বিপ্লব করছে, সারা দেশে গণশিক্ষার বিস্তার ঘটাচ্ছে, রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সার্বিক গণতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে গলা ফাটাচ্ছে, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা নারী স্বাধীনতার সপক্ষে লড়াই করছে, নারীর সমানাধিকারের কথা বলছে, ইত্যাদি। এই মডেল তাঁরা ইউরোপের কোথায় কোন কোন দেশে খুঁজে পেয়েছেন তা তাঁরাই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁদের এই কল্পিত এই মডেলের সাথে তুলনা করে যখন দেখেছেন, ভারতের সাথে তো মিলছে না, রামমোহন বিদ্যাসাগরের কাজ কর্মের সাথে মেলানো যাচ্ছে না — সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন, এখানে কোনো রেনেশাঁস টেনেসাঁস হয়নি। যা হয়েছে তা আসলে রেনেশাঁসের নামে এক রকম ক্যারিকেচার!
অথচ বাস্তব ঘটনা কী?
বাস্তবে ইউরোপের এক এক দেশে এক এক রূপে রেনেশাঁস হয়েছে। এক একটা দেশে বিশেষ ধরনের গুণী মানুষ এসেছেন। রেনেশাঁস চরিত্রদের এক একটা বিশেষ গুণের জন্য তাঁরা ইতিহাসে বরেণ্য হয়েছেন। তাঁদের কোনো দোষ ছিল না, ত্রুটি ছিল না, তাঁরা উপরে কল্পিত রেনেশাঁসের সমস্ত অ্যাজেন্ডাই পূরণ করেছেন — এরকম বাস্তবে কোনো মানুষকেই পাওয়া যায় না। কিছু উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। শেক্সপিয়রের যুগে ইংল্যান্ডে কৃষক বিদ্রোহ কোথায়? মার্টিন লুথার যিনি সনাতন রোমান খ্রিস্টীয় মত ও চর্চার বিরোধিতা করে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের জন্ম দিয়ে জার্মানিতে রিফর্মেশনের উদ্গাতা হিসাবে পরিচিত, যাঁর ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে এঙ্গেল্সও অনেক প্রশংসা করেছেন, তিনি জার্মানিতে সেই সময় সংঘটিত এক কৃষক বিদ্রোহের সরাসরি বিরোধিতা করে রাজতন্ত্রের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। সেই ঘটনাও এঙ্গেল্স দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু তার জন্য এঙ্গেল্স তাঁকে রেনেশাঁসের অন্যতম চরিত্র হিসাবে বাতিল করে দেননি। ফ্র্যান্সিস বেকনকে আমরা সকলেই হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চার প্রবক্তা বলে মানি, রেনেশাঁস যুগের যুক্তিবাদের প্রবক্তা বলে মনে করি, মার্ক্স তাঁকে আধুনিক বস্তুবাদের পিতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই বেকন ইংল্যান্ডে সুদের ব্যবসা করতেন, সুদ আদায় করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে জেলও খেটেছেন। ইতিহাস তাঁদের গুণগুলিকে মনে রেখেছে, দোষত্রুটিগুলিকে অগ্রাহ্য করেছে। গ্যালিলেও ব্রুনোর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটাও রা কাড়েননি। আজীবন ধর্মভিরু খ্রিস্টান ছিলেন। তা নিয়ে সেকালে প্রশ্নও উঠেছিল। তবু ইতিহাসে তাঁকে আধুনিক পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জন্মদাতা হিসাবে স্বীকার করা হয়। আধুনিক যুক্তিবাদী দর্শনের প্রবক্তা, বিশ্লেষণ জ্যামিতির প্রবর্তক, রনে দকার্ত তো ক্যাথলিকদের ভয়ে ফ্রান্স ছেড়ে হল্যান্ডে চলে যান এবং সেখানে রাণির ব্যক্তিগত শিক্ষকের কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে অত্যন্ত বাজে অবস্থায় মারা যান। তবু আমরা ভিতু বলে নয়, যুক্তিবাদী দর্শনের প্রবক্তা, গণিতবিদ, বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির প্রবর্তক হিসাবেই তাঁকে মনে রেখেছি। কেন না, মনে রাখার এবং মূল্যায়নের এটাই প্রকৃত পদ্ধতি।
এই সব ঘটনা যে কীভাবে বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এবাদত হোসেন, অশোক সেন, অশোক মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মার্ক্সবাদী শ্যেন চক্ষুতে ধরা পড়ল না — ভাবলে অবাক লাগে। শুধু তাই নয়। তাঁরা এক সময় তাঁদের প্রকল্পিত মডেলের সাথে মেলেনি বলে রামমোহন বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এমন প্রচার চালিয়ে গেলেন, সরোজ দত্ত আবার “শশাঙ্ক” ছদ্মনাম দিয়ে “দেশব্রতী”-র পেছনের পাতায় গালাগালি সহ এঁদের বিরুদ্ধে এমন তুই-তোকারি করে লিখে গেছেন, তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক দল যুবক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে মূর্তিভাঙার এক উন্মত্ত যুক্তিহীন কর্মকাণ্ডে মেতে উঠেছিল। যুক্তিভাঙা থেকে মূর্তিভাঙার দূরত্ব ছিল সামান্যই!
হ্যাঁ, ভারতীয় রেনেশাঁসের অনেক দুর্বলতা ছিল। ইউরোপের (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইত্যাদি) কোনো কোনো দেশের সাথে তুলনা করলে একে হয়ত ওদের তিন নম্বর কার্বন কপি বলে মনে হবে। সেই দুর্বলতার কিছু ঐতিহাসিক আর্থসামাজিক কারণ ছিল। সেই সীমাবদ্ধতাগুলো মার্ক্সবাদের আলোকে বুঝবার চেষ্টা করার দরকার ছিল। তখন ইউরোপের অন্য অনেক দেশের তুলনায় — যেমন, পর্তুগাল, স্পেন, ইত্যাদি — বাংলার রেনেশাঁস যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল বলেই হয়ত প্রতিভাত হত। মনের কষ্টকল্পিত মডেলের বাইরে বেরিয়ে এসে রূঢ় বাস্তবের দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারলে সেই সব ঘটনাবৈচিত্র্য তাঁদের নজরে নিশ্চয়ই পড়ত।
এমনকি এঁরা সকলেই রামমোহন বা বিদ্যাসাগরকে যে সেকালে “ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত শ্রেণি”-র হয়ে কাজ করার জন্য আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, খোঁজখবর নিলেই দেখতে পেতেন, ইউরোপের রেনেশাঁস নায়করাও সকলেই তাই করেছিলেন। কম আর বেশি। কেউ দু পা এগিয়ে, অন্য কেউ আবার হয়ত দু পা পিছিয়ে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির যা কিছু শক্তি এবং দুর্বলতা দেশ এবং কাল ভেদে সেই সব লক্ষণই এঁদের চিন্তা ও কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্কিমের দুর্বলতা এবং বিদ্যাসাগরের শক্তিও এই নিরিখেই বুঝতে পারা সম্ভব।
এখানে একটা কথা না বলে পারছি না। ঘোষ-দত্তর “রেনেশাঁস-হয়নি” থিসিস মেনে নিয়েও সেই দশকের বেশ কয়েকজন মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী — যেমন, বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বদরুদ্দিন উমর, নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থক, জনদরদী চিকিৎসক ডাঃ অমল ঘোষ {এনার বিস্তারিত পরিচয় আমাকে দিয়েছেন আমার ফেসবুক বন্ধু এবং বিদ্যাসাগর প্রশ্নে আমার তীব্র সমালোচক দেবব্রত চক্রবর্তী}, প্রমুখ, রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের কাজ কর্মের মধ্যে বেশ কিছু প্রগতিশীল দিক দেখতে পেয়েছিলেন। উমর সাহেবের “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ” (১৯৭৪) এবং অমল ঘোষের “মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর” (১৯৭৯) পড়লে এই ব্যাপারে আমাদের সামনে আরও একটা বিচারপথ খুলে যেতে পারে বলে আমার ধারণা। অর্থাৎ, এই “মূর্তিভাঙ্গা” দৃষ্টিভঙ্গিটি নকশাল আন্দোলনের বৌদ্ধিক উপজাত হলেও তার কোনো আবশ্যিক অঙ্গ নয়। বিশেষ করে আমরা যেন মনে রাখি, “উনিশ শতকে বাংলায় রেনেশাঁস-টাস কিছু হয়নি” মতের পূর্ব পাকিস্তানের মার্ক্সবাদী সমর্থকদের একাংশ (মহম্মদ তোঁহা পন্থীরা) যখন একই কায়দায় পাকিস্তানি শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকেও অস্বীকার করে বসলেন, তখন বোঝা গেল, নিজেদের দেশের ইতিহাস পাঠে এনাদের ক্ষমতার দৌড় আসলে কতটা। বদরুদ্দিন উমর এবং তাঁর মতো আরও অনেক মার্ক্সবাদীই সেদিন বাধ্য হয়েছিলেন এই ধরনের মার্ক্সবাদীদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত ও রক্ষা করতে।
দুঃখের বিষয়, বিনয় ঘোষ সরোজ দত্তদের শিক্ষা আমাদের সমাজের বুক থেকে হারিয়ে যায়নি। বরং তা এক নতুন কলেবর লাভ করেছে। আজকাল আর একদল পণ্ডিত দত্ত-ঘোষদের সেই কথাগুলিই বলছেন, অন্য এক প্রেক্ষিত থেকে। তাঁদের কাছে অবশ্য ইউরোপের রেনেশাঁস-টেনেশাঁসও বাজে কথা। সাদা চামড়ার লোকেরা নিজেদের বিশ্বজোড়া লুণ্ঠনের ইতিহাসকে মহিমান্বিত করে যে সব গল্পকে রেনেশাঁস বলে চালিয়েছে, ভারতে তারই প্রতিলিপিকেও একইভাবে গরিমায়িত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের মতে যুক্তিবাদটুক্তিবাদের কথা তুলে কোনো লাভ নেই। এই সবই মন ভুলানো প্রলাপন। আলোকপ্রাপ্তির যুগও নাকি এক অতিকথন। ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য আসলে ইউরোপীয়দের প্রয়োজনকেই বাকি বিশ্বের কাছে সর্বজনীন সত্য বলে চালানোর অপপ্রয়াস মাত্র! ইত্যাদি। এই চিন্তাধারা এদেশে ঢুকেছে উত্তর-আধুনিক মতাদর্শের পতাকাবাহিত হয়ে, উপনিবেশোত্তর নব্যচিন্তার নামে। {ঘটনাচক্রে, হায়, সেই ইউরোপ থেকেই! পশ্চিমি প্রভাব আমাদের বুঝি আর কাটিয়ে ওঠা কপালে নেই!!} ইংরেজ আমলের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গালমন্দ করতে গিয়ে সেকালে যা কিছু ঘটেছে, তাকে নির্বিচারে খারাপ বলে দাগিয়ে দেবার এ এক একরঙা ঐক-সংস্কৃতি। ইংরেজি ভাষা, আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক চিকিৎসা — সকলই নাকি ইউরোপের ছলনায় ভুলে আমাদের এক একটা মহাবিভ্রান্তির দ্যোতক। আমাদের ভাষা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, আমাদের ঐতিহ্যবাহিত জীবনযাপন — সবই নাকি প্রাক-ইংরেজ কালে অনেক ভালো ছিল। সুখপ্রদ এবং জনমুখী ছিল। রামমোহন বিদ্যাসাগররা সেই সব “ভালো” ধ্বংস করার কাজেই নাকি হাত লাগিয়েছেন সাদা সাহেবদের পদরেণু শিরোধার্য করে দুচারটি পদের লোভে, খেতাবের মোহে, ইত্যাদি। বিশ্লেষণ বটে, হ!
তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন, ইংরেজরা আসার আগে এদেশে নাকি এক বিশাল গণশিক্ষার আয়োজন ছিল। মেয়েদেরও নাকি অসংখ্য স্কুল ছিল। সেখানে নাকি জাতপাতের ধর্ম ও লিঙ্গের কোনো ভেদকাঠি ছিল না! অসংখ্য বিদ্যালয়ে অসংখ্য লোকের শিক্ষার সুবিস্তৃত লঙরখানা খোলা ছিল! সেই সব সহস্র বিদ্যার কেন্দ্র ধ্বংস করে দিয়ে বিদ্যাসাগর খান পঁয়ত্রিশেক স্কুল মাত্র খুলতে পেরেছেন। তাকেই নাকি এখন ঢাক পিটিয়ে বড় করে দেখানো হচ্ছে।
জয় গুরু (এরকম বাতচিত শুনলেই প্রাচীন ভক্তির উচ্চারণ ওষ্ঠদ্বারে আপনিই জেগে ওঠে)।
যদি প্রশ্ন করেন, কী করে এত সব জানা গেল? তাঁরা অ্যাডাম প্রমুখ ইংরেজ সাহেবদেরই তৈরি করা কিছু রিপোর্ট থেকে ভক্তি সহকারে উদ্ধৃতি দেন! রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সাহেব প্রীতি খুবই নিন্দার্হ, কিন্তু এনাদের সাহেব-ভক্তি একেবারে উত্তর-ঔপনিবেশিক সিন নদের জলে ধোওয়া!
ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদ (তাকেও এই নব্য-মনীষীরা কখনও কখনও নিন্দাটিন্দা করেন) উচ্চবর্ণের অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক সদস্য ভিন্ন ব্যাপকতর জনসমষ্টিকে শিক্ষাদীক্ষার বাইরে রেখেছিল, সমস্ত সামাজিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল — সে সব তাহলে মিথ্যা? সমগ্র নারীজাতিকে তারা গৃহবন্দি পর্দানশিন করে শিক্ষাদীক্ষার আলোক থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল — সেও তাহলে গুজব? ব্রাহ্মণ্যবাদই তাহলে ব্রাহ্মণ্যবাদকে খতম করে দিয়েছিল? আমরা তাহলে খামোখাই তার নিন্দা সমালোচনা করে এসেছি?
হ্যাঁ, এই প্রশ্নের সামনে পড়লে তাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদকেও ইংরেজ উপনিবেশবাদী শাসকের নির্মাণ বলে চালাতে রাজি আছেন। প্রয়োজনে বিজেপি-র হনুমন্ত বুদ্ধিজীবীদের রচনা থেকেও নির্দ্বিধায় তথ্য(?) উল্লেখ করেন! বিদ্যাসাগরকে দেশি শিক্ষার হন্তারক দেখাতে গিয়ে মনু, মনুসংহিতা, মনুবাদ (ইত্যাদি) এক আলাদিনের হাতের ছোঁয়ায় ‘নেই’ হয়ে যায়!
হ্যাঁ, এ যদি সত্য হয়, তাহলে তো সত্যিই রামমোহনের কোনো দরকারই ছিল না। শিক্ষার আলো দাউ দাউ করে জ্বলছে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, সেখানে বাল্য বিবাহ সতীদাহ ইত্যাদি হবে কেন? ইয়ার্কি পেয়েছেন? আমরা কি আর বুঝি না ভেবেছেন? এই সব হল গিয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মদের চালাকি! অপপ্রচার!
বিদ্যাসাগরকেই বা তখন লাগবে কেন?
এই সব দেখে শুনে বুঝতে পারছি, গল্প শুধু যে বিজেপি-র লোকেরা রাজস্থানে বসে বানাচ্ছে — এমন নয়। বাংলায় আমরাও কত কাহিনি তৈরি করছি। লক্ষ্য একটাই — এবং খুব মহৎ — রামমোহন বিদ্যাসাগরের কাজ, রেনেশাঁসের অর্জন, সব কিছুকে যাদুঘরে পাঠিয়ে দেওয়া।
আর — আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ্যবাদকে সম্মানজনক জায়গায় পুনর্প্রতিষ্ঠিত করা।
[৬]
বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত প্রতিটি পত্রেই শিরোনামে শ্রীশ্রী হরি শরণম্ ইত্যাদি লিখতেন। খালি গায়ে তাঁর পৈতের সুতলিও দেখা যেত। নিজের পুত্রেরও নাকি পৈতে দিয়েছিলেন খুব “ধুমধাম” সহকারে। শরীরের উপরে ছিল গ্রামীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিখুঁত প্রচ্ছদ (কিংবা পরিচ্ছদ)। সুতরাং তাঁকে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান হিসাবে দেখা এবং ভাবার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। শিশুপাঠ্য বোধোদয়ের মধ্যেও দেখা যায় ঈশ্বরের উল্লেখ এবং প্রশস্তি। জগত সৃষ্টির কৃতিত্ব প্রদান! আক্ষরিক অর্থে ধরলে এই সবই তাঁর ধার্মিক মনের কলমচিত্র বলেই মনে হবে। অন্তত আম জনতার ক্ষেত্রে এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। বহু লেখক এবং জীবনীকারও এইভাবেই তাঁকে চিত্রিত করেছেন। আজও অনেকেই করেন। অনেক বিজ্ঞজনও এভাবেই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটি সেরে ফেলেন! কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ জানা থাকলে বৃত্ত আঁকার মতোই সহজ!
আমরাও এঁকেই ফেলতাম হয়ত। কিন্তু হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল, কার্ল মার্ক্স ১৮৬৫ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির এক সভায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুনাফা কোত্থেকে আসে বোঝাতে গিয়ে কোপার্নিকাসের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, বন্ধুগণ, দুনিয়ার কোনো গূঢ় সত্যকেই উপর উপর দেখে জানা বা বোঝা যায় না! আপাত দৃষ্ট ঘটনার ভেতরে ঢুকে তলিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্লীন রহস্য বুঝবার চেষ্টা করতে হয়। এই সব সময় বুদ্ধিজীবীকেও শ্রমজীবী হতে হয়। অর্থাৎ, সত্য জলের উপর তেলের মতন ভেসে বেড়ায় না, চিনির মতো দ্রবীভূত হয়ে থাকে।
শ্রীযুত মহেন্দ্র গুপ্ত, মেট্রপলিটান স্কুলের শ্যামবাজার শাখার প্রধান শিক্ষক, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের খুব ভক্ত ছিলেন। সময় সুযোগ পেলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে দৌড়তেন। মার্ক্সের সেই পরামর্শ তো তিনি জানতেন না। ফলে তিনিও বাইরের দিকে তাকিয়ে হয়ত এক সময় ভেবেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র মশাই নিশ্চয়ই ঈশ্বর বিশ্বাসী হবেনই। হাজার হোক বামুনের ছেলে, পৈতে আছে, বৈষ্ণব বা শাক্ত না হলে মা কালীর দিকে তাঁর ভক্তিযোগ হবেই। তাঁকেও ঠাকুরের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর একবার নিয়ে যেতে পারলে কলকাতার বিদ্বৎসমাজের একটা বেশ বড় কাৎলাকে বড়শিতে গাঁথা যাবে। {উঃ, সেই কালে মার্ক্সবাদের “মুৎসুদ্দি” চরিত্রায়নটি জানা থাকলে তো শ্রীম উৎসাহে একেবারে টগবগ করতেন!} কিন্তু বেশ কয়েকবার বলেও বিদ্যাসাগরকে ঠাকুর বা দক্ষিণেশ্বর সম্পর্কে একটুও আগ্রহী করা গেল না! “হবে’খন” “যাব’খন” “আচ্ছা, সে একদিন নিশ্চয় যাওয়া যাবে”, “চেষ্টা করব” — ইত্যাকার অনিশ্চিত-প্রতিশ্রুতি সুলভ সৌজন্যের আড়ালে বিদ্যাসাগর সেই যাওয়াটা মুখে একেবারে বাতিল না করলেও পৌনপুনিক ভাবে স্থগিতই রেখে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আমরা এখন তো জানিই, তাঁর সেই যাওয়াটা চির-স্থগিত থেকে গিয়েছিল।
কী আর করা, মহম্মদ যখন পর্বতের কাছে যাবেন না, পর্বতকেই তাহলে বলে-কয়ে মহম্মদের কাছে নিয়ে আসতে হয়। আর, সকলেই জানেন, প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও, মুর্ছাব্যামো থাকলেও, গদাধর চট্টোপাধ্যায় খুব বড় মাপের একজন সংগঠক ছিলেন। তিনি সেই সময়ের কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রায় সবাইকেই তাঁর শিষ্য বা ভক্ত বা গুণমুগ্ধ বানিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর এই ভক্ত রিক্রুটের মন্ত্রটি ছিল “যত মত তত পথ” ফরমুলা। বিদ্যাসাগরের মতো তিনি “সত্য এক” বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে সত্য বহু। অন্তত বহু-বচন! স্বয়ং ঋগবেদ বলেছে — “একম্ সদ্বিপ্রাঃ বহুদাবদন্তি।” ফলে সত্যের বহু-বচনে দোষ নেই। এ ছিল এক আদর্শ কালপূর্ব অগ্রিম উত্তর-আধুনিক তত্ত্বক্রম (paradigm)। এছাড়া, তাঁর সরল বাক্যালাপ, সহজিয়া পল্লি-উদাহরণ, শিশুর মতো হাসি — সব মিলিয়ে তিনি বহু মানুষকেই জয় করেছিলেন। কিন্তু তখনও বাকি থেকে গেছেন একজন — বিদ্যাসাগর। তাঁকে দখলে নিতে পারলে বিরাট সাফল্য। অতএব রামকৃষ্ণ মহেন্দ্রবাবুর মাধ্যমে দিন ক্ষণ সাব্যস্ত করে একদিন বাদুড়বাগানে চলে এলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে।
সে এক অভূতপূর্ব আলাপন। ঘন্টা চারেক ধরে। বক্তা মাত্র একজনই। তিনিই খালি বলে চললেন। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। শ্রোতা অবশ্য দুজন। তার মধ্যে একজন আবার বিমুগ্ধ শ্রোতা। যাই শোনেন, অমৃতের সন্ধান পেতে থাকেন। আর অন্য জন ক্রমান্বয়ে আগত বাক্যশব্দের এক নিঃশব্দ পরম গ্রাহক। সে যুগে অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্নোত্তর চালু থাকলে সংলাপ বজায় রাখার সৌজন্যের স্বার্থে বিদ্যাসাগরের উত্তরগুলি এক আদর্শ সংগ্রহ হয়ে থাকতে পারত। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর খাওয়াদাওয়ারও ভালো বন্দোবস্ত করেছিলেন। রামকৃষ্ণও খেয়েদেয়ে খুশি হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের যত পথ জানা ছিল, বিদ্যাসাগরের মত অনুমান করে করে সেই অনুযায়ী প্রচুর ঢিল ছুঁড়েছিলেন সেদিন। একটাও লক্ষ্যভেদ করল না। আধ্যাত্মিক লাইনের কোনো পথেই বিদ্যাসাগরের মতের নাগাল পেলেন না তিনি। ভদ্রতা ও বিনয়ের অবতার {অবতার শব্দটা বোধ হয় এখানে বেমানান, বরং রাহুল দ্রাবিড় বলাই ভালো} হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিটি ঢিল যত্ন করে হাতে ধরে নিয়ে বিস্মৃতির আলমারিতে চালান করে দিলেন।
রামকৃষ্ণ বুঝলেন, এখানে আসা তাঁর ব্যর্থ। অনেক দিনের পোষিত ইচ্ছা পূরণ হল না। তবু বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেই তিনি আমন্ত্রণ জানালেন বিদ্যাসাগরকে রাণি রাসমণির “বাগান” দেখতে আসার জন্য। এই একটি আমন্ত্রণ বাক্যেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে তিনিও বুঝে গেছেন — বিদ্যাসাগরের আরাধ্য বিষয়টি ঠিক কী ধরনের।
ভক্তিবাদীরা অনেকেই বিদ্যাসাগরের “মৃদু মৃদু হাস্য” এবং বিনয় ব্যঞ্জক কথার ভিত্তিতে ভেবেছেন এবং দাবিও করেছেন, বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণের গূঢ় আধ্যাত্মিক কথার গভীরতায় নাকি বিমোহিত ও নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। এতে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাঁরা অন্তত তাঁদের গুরুদেবের মতো বুদ্ধিমান নন। আমন্ত্রণ বাক্যটি যে পরাজিতের সুচিন্তিত সমঝোতাপত্র, তা তাঁরা ধরতেই পারেননি। পরবর্তীকালে তিনি যে কোনো দিনই সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন না, তাও তাঁরা লক্ষ বা উল্লেখ করতে ভুলে যান। রামকৃষ্ণ কিন্তু বুঝে গিয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র আর কখনই ওমুখো হবেন না। মহেন্দ্র গুপ্তকে অনেক বার তিনি প্রশ্ন করেছেন, বিদ্যাসাগর আসবেন বলেও এলেন না কেন? তারপর “কর্মের অহঙ্কার”, “রজোগুণ বেশি”, “মিথ্যেবাদী”, ইত্যাদি বলে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় বেশ কিছু ইয়ে শব্দ উচ্চারণ করেছেন।
এই ঘটনাটা এত সবিস্তার বলার কারণ, প্রচলিত ধর্ম প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গিটি চেনানো। তিনি কোথাও কিছুই তাঁর মত হিসাবে সরাসরি লিখে যাননি। ভারতীয় আস্তিক দর্শনসমূহ সম্বন্ধে অবশ্য তাঁর মতটা আমরা আগেই জেনেছি। দেখেছি যে প্রচলিত কোনো দর্শনেই তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। আর, বিরুদ্ধ চিন্তার প্রতিনিধিকে পাশে রাখলেই যে আলোচ্য ব্যক্তির মত সবচাইতে ভালোভাবে ফুটে ওঠে এ তো সকলেই বোঝেন। আমরা আরও একবার শিখলাম যে খালি চোখে দেখে যা মনে হচ্ছে তা সব সময় সত্য হয় না!
মহেন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাসাগরের আরও কিছু সংশয়াত্মক সংলাপ সংরক্ষণ করেছেন। একবার সেন্ট লরেন্স নামক এক বড় ব্রিটিশ জাহাজ মাঝ-সমুদ্রে ডুবে গিয়ে যাত্রী এবং নাবিকদের মিলিয়ে অনেক লোকজন মারা গেল। সংবাদপত্রে সেই খবর দেখে ঈশ্বরচন্দ্র নাকি প্রকাশ্যেই কারও কারও কাছে আক্ষেপ করেছিলেন, এতগুলো নিরপরাধ মানুষকে এই ভাবে জলে ডুবিয়ে মেরে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কোন সদিচ্ছা ব্যক্ত হল! ঈশ্বরের পরম ভক্ত শ্রীম-র বোধ হয় খুব গায়ে লেগেছিল কথাটা। গুরুদেবের কাছে নালিশ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, পাণ্ডিত্যের অত গর্ব ভালো নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার আমরা আর কতটুকুই বা বুঝি?
ঐশ্বরিক শক্তিতে আস্থাবান হলে পরমহংসের এই উত্তরটা কিন্তু চমৎকার যুক্তিপূর্ণ বলে বোধ হবে! সত্যিই তো। সমুদ্রের হাঙর জাতীয় মাংসাশী প্রাণীগুলিও তো ঈশ্বরেরই সন্তান। বছরে এক আধদিন তাদেরও ভালোমন্দ খেতে সাধ জাগে। পরমেশ্বরকে তাদের কথাও এক একদিন ভাবতে হয় বৈকি! হয়ত সেদিন ইশ্বরের এরকম ইচ্ছাই হয়েছিল। কে বলতে পারে! বিদ্যাসাগর তাঁর অধার্মিক পার্থিব সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ চেতনায় নিশ্চয়ই অত দূর অবধি আর চিন্তাকে প্রসারিত করতে পারেননি। নিছকই মানুষের ইহলৌকিক ভালোমন্দের কথা ভেবেছিলেন।
ব্যালান্টাইনের যে সুপারিশ নিয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিরোধ হয়, তার পেছনেও রয়েছে এই একই পার্থিব ইহলৌকিক ধর্মনিস্পৃহ মনোভাব। বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইন চান আইরিশ বিশপ জর্জ বার্কেলের An Inquiry into Human Knowledge বইটা কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য করতে। তিনি মনে করেন, এর ফলে ভারতীয় ছাত্ররা যখন দেখবে, বার্কেলের দর্শনের সঙ্গে বেদান্তের চিন্তার খুব সাদৃশ্য রয়েছে, তারা ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে। মোদ্দা কথা হল, ব্যালান্টাইন ভারতে ভাববাদী চিন্তাভাবনারই ডালপালা ছড়াতে চাইছিলেন। আর সেই জন্য তিনি আবার জন স্টুয়ার্ট মিলের Logic বইটা পুরো না পড়িয়ে এর একটা সারাংশ (যা আবার তিনিই নাকি তৈরি করেছিলেন) পড়ানোর সুপারিশ করেছিলেন!
বিদ্যাসাগরের ঠিক এই জায়গাতেই আপত্তি। সাদৃশ্য যাই থাকুক, দুটো দর্শনই তো আসলে ভ্রান্ত এবং ভাববাদী। বার্কেলে শেখাচ্ছেন, দুনিয়াটা আসল নয়, আমাদের মনের সৃষ্টি। সংবেদন গুচ্ছ থেকে প্রাপ্ত। আমরা যেমন ভাবি, বস্তুজগতকে তেমনই মনে হয়। বাস্তবে আমাদের চেতনার বাইরে স্ব-অস্তিমান বস্তুজগত বলে কিছু নেই। (শাঙ্কর) বেদান্তও বলে, এই জগতটা মায়া, অধ্যাস মাত্র। স্বপ্ন দর্শন তুল্য বিভ্রম। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়। নানা কারণে তা সত্ত্বেও বেদান্ত আমাদের পাঠক্রমে রেখে পড়াতেই হবে {বিদ্যাসাগরের কালে এর ব্যতিক্রম করে কিছু ভাবা বা করা সম্ভব ছিল না; এখনও সম্ভব কিনা ভেবে দেখতে হবে}। সেই সঙ্গে ইউরোপের এমন সমস্ত দর্শন পড়াতে হবে, যাতে চিন্তার ক্ষেত্রে বেদান্তের মায়াবাদের বিরুদ্ধে কিছুটা মনন-টীকাকরণ হয়ে যায়। প্রতিষেধক হিসাবে। তাই তিনি বার্কেলের রচনা সিলেবাসে একেবারেই রাখতে চান না। আর মিলের বইটা গোটাটাই পাঠ্য করতে চান! যাতে ভাববাদী চিন্তাভাবনার ডালপালা ছাড়ানো যায়!
ছড়ানোর বদলে ছাড়ানো! সার্থক বিপরীতার্থক উদ্দেশ্য একেই বলে।
এই চিঠিগুলো সরকারি ফাইলে চাপা পড়ে থাকায় অনেক দিন পর্যন্ত এদেশের লোকে বিদ্যাসাগরের মগজটিকে চিনতে পারেনি। পরে যখন (১৯২৬) জানাজানি হল, তার পরও অনেকেই চেষ্টা করেছেন, এই বিষয়ে আলোকপাত না করতে। এখানে আবার আমাদের বিনয় ঘোষের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতেই হয়। ১৯৫০-এর গোড়ায় তিনি তিন খণ্ডে “বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ” লিখে এই চিঠিগুলির মর্মার্থ বৃহত্তর বাঙালি পাঠকের দরবারে যথার্থ বিশ্লেষণ সহ তুলে ধরেছিলেন। তখনও তিনি বাংলার রেনেশাঁসে বিশ্বাস রাখতেন। ১৯৬৮ সালে যখন তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বোধিতে “ভ্রম নিরসন” করে “জ্ঞানী বুদ্ধ” হয়ে বসলেন, তার সামান্য কিছুকাল আগেই — আমার মতো অনেক অভাজনেরই — তাঁর হাত ধরেই বিদ্যাসাগরকে চেনা হয়ে গেছে। সেই বিভ্রম আমাদের এখনও কাটেনি। বরং অটুট ভক্তি জন্মে গেছে।
ব্যালান্টাইনের কেন বার্কেলে এত পছন্দ ছিল — এই প্রশ্নের চাইতেও আমাদের কাছে শ্রেণিস্বার্থ বিচারের দিক থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের কেন ব্যালান্টাইনের মতটা অত পছন্দ হয়েছিল। তাদেরই “দাসানুদাস” বিদ্যাসাগরের যুক্তি কেন তাদের মনে ধরল না? দত্ত-ঘোষের ঠুলি পড়ে আমরা আজও বুঝি বা না বুঝি, ইংরেজরা এই দেশে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের দীর্ঘায়ু কামনায় শ্রেণিগত নাসিকায় ঠিকই বুঝেছিল, ভারতীয় ছাত্রদের ঠিক কী ধরনের শিক্ষা দিলে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। বিদ্যাসাগরের সুপারিশগুলি দেখেই তারা বুঝে নিয়েছিল, এই লোকটা তো আসলে তলে তলে আমাদের সর্বনাশ করতে চায়। আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে চায়! ছাত্রদের বস্তুবাদ যুক্তিবাদ শেখাতে চায়! আগামী প্রজন্মকে যুক্তিবাদী বিচারশীল করে তুলতে চায়! ব্যালান্টাইন তো ঠিকই বলেছে। জগতটাকে মায়া বলে ভাবতে শেখানোই তো ভালো। এই বিশাল উপনিবেশটাকে বেশ পাকাপোক্ত করে “মায়া”ভরে অনেক দিন ধরে নিশ্চিন্তে শাসন ও দোহন করা যাবে।
এর পরের “সুতরাং”-লাঞ্ছিত বাক্যটি নিয়ে আশা করি কারওই কোনো আপত্তি হবে না।
চতুর্থ পর্ব এই লিঙ্কে
লেখক পরিচিতি: ‘সেস্টাস’ নামে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক। বিজ্ঞান ও মার্কসবাদের আলোয় বিজ্ঞানের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে লোকপ্রিয় প্রবন্ধের লেখক।


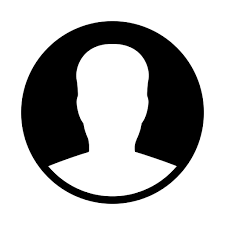
আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ওনার কর্মকান্ড ও চিন্তার ফ্রতি এরুপ আলোকপাত করার জন্য ধন্যবাদ। পরের অংশের জন্য অপেক্ষায় থাকলাম।