সমসাময়িক গণমাধ্যম ও লেখালেখিতে যে ধরনের শ্রম-বিযুক্ত খাদ্য, থুড়ি, পণ্যপূজার নমুনা দেখা যায়, যার মধ্য দিয়ে বিপুলভাবে মহিমান্বিতও করা হয় গার্হস্থ্য শ্রমের লিঙ্গায়িত বিভাজনকেও, তার মধ্য দিয়ে সর্বজনীনক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এক ধরনের অনৈতিহাসিক, অপার্থিব মাতৃত্বকে। সেই সমস্ত রূপায়ণের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, সমসাময়িক খাদ্যসাহিত্য কি তবে এক ভাবে হয়ে উঠছে আমাদের ক্রমশ পিছোতে থাকা সময়েরই প্রতিভূ? যেখানে, বকলমে হৃত খাদ্যবস্তুর নাম করে তৈরি হয় ‘রান্নাঘরই মেয়েদের প্রধান জায়গা’ জাতীয় মতাদর্শগত বলয়? এবং, সেই বলয়ের কেন্দ্রে থাকে এক ধরনের পণ্যায়িত মাতৃত্ব-বন্দনা? এর বিপরীতে, অন্যধরনের খাদ্য-সাহিত্য বা গণমাধ্যমের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে গেলে ঠিক কী ধরনের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক শ্রম দিতে হবে আমাদের? লিখেছেন নন্দিনী ধর।
বাংলার ‘প্রথম আন্তর্জাতিক ফুড ম্যাগাজিন’ ‘হ্যাংলা’-র ওয়েবসাইটে গেলে, আরও বিবিধ ধারার খাদ্যবিধি, যেমন ‘বাঙালি রান্না’, ‘হারিয়ে যাওয়া রান্না’, ‘মহাদেশীয় রান্না’–র সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আরেকটি বিশেষ ধারা – ‘মায়ের হাতের রান্না’। সেই ধারার লিংকে গেলে দেখা যায় অদ্ভুত একটি মিশ্রণ। সেখানে যেমন আছে ‘মাটন কোফতা’, বা ‘বেলের বরফি’, তেমনই রয়েছে ‘মাটন মালাবার’ বা ‘জাফরানি ফুলকপি’। অর্থাৎ, এই ধারার অন্তর্গত খাদ্যদ্রবগুলির কোনও ভূগোল নেই। আমিষ না নিরামিষ না মিষ্টান্নজাত, তারও কোনও ঠিকঠিকানা নেই। আছে কেবল মায়ের হাতে উৎপত্তির গল্প। তাও আবার কার মা, কোথাকার মা সেসবের কোনও হদিশ নেই। ‘মা’ এখানে হয়ে ওঠেন একটি সর্বজনীন একক—ইতিহাসবিহীন, ভূগোলবিহীন, বাকি সামাজিক পরিচয়হীন।
অবশ্য, শুধু ওয়েবসাইটে নয়, সময়ে সময়ে — প্রায় বছরে একটি করে — ‘মায়ের হাতের রান্না’ জাতীয় একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক এককটিকে এক ধরনের বিশেষ মান্যতা দেয় পত্রিকাটি। প্রধানত ‘মাদার্স ডে’-কে কেন্দ্র করে।
এখানে উঠতে পারে একটি গভীরতর প্রশ্ন। ঠিক কবে থেকে আমাদের বাংলা তথা ভারত তথা উপমহাদেশের ক্যালেন্ডারে যুক্ত হল ১৪ মে-র মাতৃদিবস? যা কিনা সাধারণভাবে পরিচিত ছিল আসলে একটি মার্কিনি ঐতিহ্য বলে? বলার অপেক্ষা রাখে না, খুবই সাম্প্রতিক এই মাতৃদিবস, থুড়ি, মাদার্স ডে নিয়ে সমাজজোড়া এই কলরোল। এই যে নিত্যনতুন ক্যালেন্ডার নির্মাণের গল্প, সেখানে কি তবে আসলে বিরাজ করে এক ধরনের গভীর সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের পরিমণ্ডল? যা আসলে নির্ধারিত করে দেয় একেকটি দিবস-দৃশ্যমানতা, সংগঠিত করে সামাজিক গণমাধ্যমের হৈ হৈ রৈ রৈ? সেই হিসেবে, আমাদের মাকে ভালোবাসার দিনও এসেছে নয়া-উদারনীতির হাত ধরে, নয়া-উদারনৈতিক ক্যালেন্ডারের হাত ধরে। যেখানে, টিভিজাত বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে গ্রিটিংস-কার্ড কোম্পানি হয়ে অনলাইন কেনাবেচার পোর্টালগুলি ঠিক করে দেয়–আমাদের আবেগের নির্দিষ্ট সময়, প্রিয়জনদের ভালোবাসা জানানোর পদ্ধতি ও দিনক্ষণ। এবং, এই যে নয়া-উদারনৈতিক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের পরিমণ্ডল, সেখানে যুক্ত হয় খাদ্যসংস্কৃতির মতো তথাকথিত ‘নিষ্পাপ’ ও অরাজনৈতিক ক্ষেত্রও। এবং, কোথাও একটা এই যে পত্রিকাটির নিজেদের ‘আন্তর্জাতিক’ বলে ঘোষণা, সেটাও যেন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের নিয়মে, এই নয়া-উদারনৈতিক ঘড়ি ধরে, ক্যালেন্ডার পুনর্নির্মাণের প্রয়াসের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। তাই, বলতে বাঁধা নেই, ‘হ্যাংলা’ পত্রিকাটি নির্মীয়মান বাংলা ও বাঙালির নয়া-উদারনীতিবাদের প্রতিভূ। এবং, নয়া-উদারনীতিবাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উত্থানের হাত ধরাধরি করে যে পৃথিবীতে ঘটেছে খাদ্য বিষয়ক গণমাধ্যমের বিস্ফোরণ, ‘হ্যাংলা’ পত্রিকাটির উত্থানও সেই বিস্ফোরণের হাত ধরেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।
এ কথার অবতারণা বিশেষত এই কারণে যে পত্রিকাটির মধ্যকার যে উপস্থাপনা সমূহ, তাদেরকে ‘সাবেকি’ বা ‘ঐতিহ্যমণ্ডিত’, ‘ট্রাডিশনাল’ বলে উড়িয়ে দেবার কোনও জায়গা নেই। বরং, সে সব রূপায়ণকে দেখতে হবে বর্তমান নয়া-উদারনীতিবাদের সাংস্কৃতিক রাজনীতির নিরিখেই। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই, বর্তমান প্রতিবেদনে ‘মায়ের হাতের রান্না’ নামের যে লক্ষ্মণা বা ট্রোপটি বারবার ফিরে এল, তার আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমেই বলা ভালো, অবশ্য, পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলী বা কর্মকর্তারা এই ‘মায়ের হাতের রান্না’ নামক বিষয়টির উদ্ভাবনা ঘটিয়েছেন, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং, বলা ভালো, সামাজিকভাবে বহুল প্রচারিত একটি বিষয়কে—একটি আবেগকে, একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক লক্ষণাকে—তাঁরা আরও একবার সর্বসমক্ষে নিয়ে এসেছেন। নিজেদের মতো করে মোড়কে মুড়ে পাঠকদের সামনে হাজির করেছেন।
যেমন, ভেবে দেখুন, এই উপমহাদেশের বহু ভাষায়, ‘মায়ের হাতের রান্না’ শব্দবন্ধগুলি একটি অন্য অনুরণন নিয়ে সামাজিক ভাবে হাজির হয়। হিন্দিতে ‘মা কি হাত কি ডাল’, বা বাংলাভাষায়, ‘মায়ের হাতের রান্নার সে স্বাদ’, ইত্যাদি জাতীয় যে বহুল প্রচলিত শব্দবন্ধ, কোথাও যেন আমাদের কাছে নিয়ে আসে একটি সুখী গৃহকোণের ছবি, যে সুখী গৃহকোণ টিকে আছে যাবতীয় সামাজিক সংঘাতের বাইরে, একটুকরো স্নিগ্ধ গার্হস্থ্যতার প্রতিভূ হয়ে। মায়ের হাতের রান্না সেই সুখী গৃহকোণেরই সশরীরী, মূর্ত বস্তু প্রতীক হয়ে। সেই শব্দবন্ধে ‘মা’ মানুষটিরও একটি চরিত্রায়ন হয় বইকি। মা এখানে সর্বংসহা, সদা হাস্যময়ী, সংসার ও সন্তানের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তদুপরি, মায়ের স্নেহের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছেদভাবে জড়িয়ে থাকে তাঁর রন্ধনপটীয়সীতা। এই সদাহাস্যময়, সন্তানের জন্য রন্ধন নিবেদিত প্রাণ, সর্বংসহা চিত্রটি বাদ দিলে, বাকি মা’র চিত্রায়নটি অবশ্য হয় অতীব ভাসা ভাসা, অস্পষ্ট। সেখান থেকে মা মানুষটি কেমন, তা বের করা অতীব দুরূহ ব্যাপার।
অন্যদিকে আবার, রান্নার বইয়ের যে পেশাগত জগৎ, সেখানেও ‘আমার মায়ের রান্নাঘর’ একটি সুপরিচিত লিখন ও সংকলন ধারা। যেমন ধরুন, সুবিখ্যাত শেফ সঞ্জীব কাপুরের রন্ধনপ্রণালীর সংকলন-বই — ‘কুকিং উইথ লাভ : ভেজেটেরিয়ান রেসিপিস ফ্রম মাই মাদার্স কিচেন।’ বইটির উপসংহারে শেফ কাপুর একটি ছোট্ট কবিতা লিখলেন :
“Each morning as I struggle to wake up
Aromas from the kitchen make me sit up.
I then follow my nose and watch my mother cook
Mouth-watering dishes though she never refers to a book.
She adds a pinch of this and a dash of that,
Ah yes! Plenty of love, no lack of that!”
কবিতা হিসেবে যে এটি কোনোভাবেই উৎকৃষ্টমানের নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, কবিতাটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল কতগুলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্য। প্রথমত, অন্দরমহলের যে রান্নাঘর, সেখানে রয়েছে রান্না করার একটি নিজস্ব পদ্ধতি। সেখানে লিখিত রন্ধনপ্রণালীর বড়ো একটা প্রয়োজন নেই। আগুন ও উপকরণের রসায়নের ওপর দাঁড়িয়ে যে রন্ধনকার্য সমাপ্ত হয় গৃহাভ্যন্তরে রান্নাঘরে, সেখানে স্মৃতিই যথেষ্ট। এমনিতে, পেশাদারি খাদ্য জগতে, এই ধরনের স্মৃতিনির্ভর ঘরোয়া রান্নার জন্য একটি শব্দ ব্যবহার করা হয় –‘আন্দাজ’। পেশাদারি রাঁধুনে, থুড়ি, শেফদের রন্ধনপদ্ধতি যদি দাঁড়িয়ে থাকে যথাযথ, নির্দিষ্ট, যথাযথ লিখিত উপকরণ মাপের ওপর, মেয়েদের অন্দরমহলের রান্না দাঁড়ায় স্মৃতির ওপর, চোখের চাউনির ওপর, ঘ্রাণশক্তি, খাদ্যবস্তুর রঙ, হাতের স্পর্শের অনুভবের ওপর। অর্থাৎ, এই যে মেয়েদের রান্নার পদ্ধতি, সেখানে কোথাও একটা রয়ে গেছে আধুনিকতা-বহির্ভূত একটি সংস্কৃতি। যে আধুনিকতা চায় সবকিছুকে মাপবন্দি করতে, কালিবন্দি করতে, লিখিত দলিল, প্রমাণপত্রে পর্যবসিত করতে। আর আছে, ভালোবাসা। অপার ভালোবাসা। যা নাকি হেঁশেলের রসায়নের সাথে মিলেমিশে গিয়ে মায়ের হাতের রান্না বিষয়টিকে করে তোলে মায়াময়, অলৌকিক।
এবং, এই ‘ভালোবাসা’ নামের উপকরণের মধ্যেই রয়েছে একটি গভীর মতাদর্শগত বক্তব্য। যদিও, তা হাজির হয়েছে একাধিক সাংস্কৃতিক উপাচারে মুড়ে। মানে, সঞ্জীব কাপুর নিজে শেফ। রন্ধনশিল্প তাঁর পেশা। রন্ধনপ্রণালীর বই লেখাও। সেখানে রন্ধনকার্য তাঁর কাছে শ্রম, পুঁজির বিনিময়ে করা মেহনত। অর্থাৎ, সঞ্জীব কাপুরের কাছে রন্ধনশিল্প, বা সেই শৈল্পিক শ্রমের যে ফসল, অর্থাৎ রন্ধনকৃত যে খাবারদাবার, তা ব্যবসায়ের নিয়মান্তর্গত। একইভাবে, যে রন্ধনপ্রণালীর সংকলনগ্রন্থটি তিনি লেখেন, তাও বাজারে বেরোয় একটি পণ্য হয়ে। যার থেকে সঞ্জীব কাপুরের পারিশ্রমিক আসে।
অন্যদিকে, মা-র হাতের রান্নায় তেমন কোনো ব্যবসায়িক প্রকল্প নেই। তার স্থান নিয়েছে ‘ভালোবাসা’ নামক পুঁজি-বহির্ভূত এককটি। তাই, আরেকটু তলিয়ে ভাবতে গেলে, ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় একটু জটিল। ‘মায়ের হাতের রান্না’ বিষয়টি আসলে কি তবে কোনও এক ভাবে আমাদের কাছে নিয়ে আসে এক ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক অবচেতনের দ্যোতনা? যেখানে আমরা আপাদমস্তক পুঁজিমোড়া জীবন কাটিয়েও খুঁজি পুঁজিবহির্ভূত গলিঘুঁজি ‘মায়ের হাতের রান্না’ কি তবে হয়ে ওঠে সেই অনুসন্ধানেরই উপসর্গ?
যেমন ধরুন, ২০১৬ সালের ‘মাদার্স ডে’ সংখ্যা। সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ বা কভার স্টোরির শিরোনাম, ‘মায়ের হাতের ম্যাজিক’। তা নিয়ে লিখতে গিয়ে সম্পাদকরা লিখলেন ছোট্ট একটি মুখবন্ধ :
“পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যাজিশিয়ান মা। মায়ের হাতের ওই জাদুকাঠিটা থাকে না ঠিকই, তবে অদৃশ্য জাদুকাঠির ছোঁয়ায় সব খারাপকে ভালো, না পাওয়ার যন্ত্রণাকে হাসিতে, আর হঠাৎ লোডশেডিংয়ের মতো অন্ধকারে আলো জ্বালায় মা। মায়ের মতোই তুলনাহীন তাঁর হেঁশেলের জাদুমন্ত্রও। হাত ধুয়ে জল দিলেও সে ব্যঞ্জন হয়ে যায় অমৃত সমান। যতো বড়ো রেস্তোরাঁতেই যাই না কেন, এক দিন-দু’দিন বাদে মায়ের হাতের স্বাদ চাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে স্বাদগ্রন্থি।”
উল্লেখযোগ্যভাবে, এইখানে ‘ভালোবাসা’ শব্দটি নেই। তার বদলে আছে, ‘জাদু’ শব্দটি—বিভিন্ন রকমফেরে। এবং, এক্ষেত্রে, ‘জাদু’ শব্দটির মধ্যে বেশ একটা মজা আছে। শব্দটা শুনলেই মনে হয়, এক নিমেষে ঘটে যাওয়া পরিবর্তন। যেখানে শ্রম নেই। শ্রমজাত স্বেদরক্তের কোনও গল্প নেই। ‘জাদু’ শব্দটি মা’র রান্নাঘরের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে তাই ভুলিয়ে দেওয়া যায় হেঁশেলজাত মায়েদের/মেয়েদের শ্রম। রান্নাঘরের তাপ, ঘাম, বিপদ, আঘাত, আগুন। অন্যদিকে, রেস্তোরাঁর খাবারের সাথে মায়ের হাতের রান্নার তুলনা করে এক ধরনের বৈপরীত্য, এক ধরনের দ্বৈততা তৈরি করা হল এখানে। যে দ্বৈততা সঞ্জীব কাপূরের উপস্থাপনায় এসেছিল নিরুচ্চারে, সেই দ্বৈততাকেই–অর্থাৎ, ঘরোয়া খানা/ মায়ের হাতের রান্না বনাম রেস্তোরাঁর রান্না/ ব্যবসায়িক রন্ধনসংস্কৃতি—হাজির করা হল সজোরে, সশব্দে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে। এবং, বছর বছর এই দেখিয়ে দেওয়াটা চলতেই থাকল। যেমন ধরুন, ২০১৯-এ ওই একই ‘মাদার্স ডে’ সংখ্যা, যার নাম ‘মায়ের রান্না’ তার মুখবন্ধে লেখা হল :
“সকাল থেকে রাত অবধি যে মানুষটার ওপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায় তাকে আমরা ‘মা’ বলেই ডাকি। বাড়ির যাবতীয় কাজ দশভূজার মতোই যে সামলায় আমাদের মায়েরা। বিশেষত ভোজের ক্ষেত্রে। ব্রেকফাস্ট- লাঞ্চ-সন্ধের খাবার-ডিনার, সব সময়ের নানা ধরণের নানা পদ মুখের সামনে তুলে ধরেন, সঙ্গে মন ভোলানো হাসি ফ্রি। আর সেসব পদের স্বাদ, আহ অমৃত। সারা দুনিয়ার সেরা সেরা রেস্তোরাঁর চোখে দেখলেও সে স্বাদ যেন মায়ের হাতের ধারেকাছেও পৌঁছয় না।”
এবং, এইবার বাকি আরও সবকিছু–মায়েদের দুর্দান্ত রন্ধনপটীয়সীতা, স্নিগ্ধতা, সন্তানের জন্য সদাসর্বদানিবেদিত প্রাণ—এ সবের সাথে যোগ হল মায়ের বিনামূল্যের হাসি।
অবধারিতভাবে, এই সমস্ত উপস্থাপনার যোগফল খুঁজলে দেখা যাবে এক ধরনের বিশেষ রূপায়ণ মা চরিত্রটির। সেখানে মা দেবীসমা, সুস্বাদু রান্নার মেশিন, সে সব খানা তিনি আবার বেড়ে দেন সন্তানদের পাতে হাসিমুখে। অবশ্য, না ‘হ্যাংলা’ পত্রিকার পাতা, না সঞ্জীব কাপুরের বইতে আমরা পেলাম রান্না সম্পর্কে মায়েদের নিজেদের বয়ান। যদি-বা সঞ্জীব কাপুর শেষ পৃষ্ঠায় নিজের মা ও শ্মশ্রুমাতার ছবি দিয়ে মা-দের ‘দেবী’ থেকে নামিয়ে মূর্ত মানবীর চেহারা দিলেন, ‘হ্যাংলা’ র এই বিশেষ সংখ্যাগুলির পাতায় সেটুকুও দেখা গেল না। মায়েরা হয়ে রইলেন বিমূর্ত, ভৌতিক উপস্থিতি, যাঁদের আমরা চিনতে শিখলাম পরোক্ষভাবে—তাঁদের সন্তানদের বয়ানে।
তৎসহ, আরও একভাবে চিনতে শিখলাম তাঁদের। তা হল, তাঁদের শ্রমের ফসলের রূপায়ণ থেকে। অর্থাৎ, তাঁদের বানানো খাদ্যসামগ্রী থেকে। এখানেও অবশ্য ঠিক প্রত্যক্ষভাবে পেলাম না তাঁদের। পেলাম তাঁদের পুত্রসন্তানরা—যাঁরা কিনা পেশাগত রাঁধুনি, শেফ—তাঁদের সৃষ্টির আলোকচিত্রের মাধ্যমে। তাঁরাই তাঁদের মায়েদের রান্না করা খাবার নতুন করে রাঁধলেন, তাঁর ছবি তুললেন, রন্ধনপ্রণালী লেখার নিয়মবিধি মেনে রন্ধনপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করলেন, এবং পত্রিকার পাতায় বা বইয়ে ছাপালেন। সঞ্জীব কাপুর যেমন নিজেই জানালেন, তাঁর মা ও শ্মশ্রুমাতার রান্না করা খাবার বিক্রয়যোগ্য রেসিপিতে বানাতে হাজির ছিলেন গোটা একটি টিম।
এর মধ্যে দিয়ে অবশ্যম্ভাবীভাবে এক ধরনের স্বীকৃতি দেওয়া হল মেয়েদের সৃষ্টিশীলতাকে। যে সৃষ্টিশীলতা ঐতিহাসিকভাবে শিল্প বলে স্বীকৃতি পায়নি বৃহত্তর সমাজ বা শিল্পজগতের কাছে, কিংবা রন্ধনশিল্পের যে পেশাদারি জগৎ, সেখানেও। কিন্তু, এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে এল বেশ কিছু প্রশ্নও। যেমন, স্মৃতি বা ‘আন্দাজ’—এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের রন্ধনশিল্পের জগতের থেকে নির্যাসটুকু নেওয়া হল, নিয়ে সেই সমস্ত খাবারের রন্ধনপ্রণালী লিপিবদ্ধ করে, মাপজোকের আওতায় এনে তাঁদের ওপর একই সঙ্গে আরোপ করা হল আধুনিকতার, বাজারের সর্বগ্রাসী প্রমিতকরণ, নিয়মাবলী। যে প্রমিতকরণের জগৎ-বহির্ভূত বলেই, এই ঘরানার রন্ধনশিল্পকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছিল এক ধরনের রোমান্টিকতা।
এমনিতেই, খাদ্য-গণমাধ্যম, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল রন্ধনপ্রণালীর সংকলন—চলতি ভাষায় রান্নার বই—তৈরি করেছে একধরনের বিশেষ দৃশ্যমানতার নান্দনিকতা। সে নান্দনিকতা অনুসারে, খাবারের ঝলরমলর ছবিই বহুক্ষেত্রে হবে রান্নার বই সমূহের মূল উপজীব্য। অর্থাৎ, সেই ছবিগুলোর কাজ হবে এক ধরনের চোখের খিদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎপাদন। সাধারণভাবেই তাই দেখা যায়, রান্নার বইয়ের যে জীভ, থুড়ি, চোখের লালা ঝরানো ছবি, সেখান থেকে উধাও শ্রমের সমস্ত চিহ্নমাত্র। এক ভাবে বলতে গেলে, সাবেকি উদারনৈতিক পুঁজিবাদের হাত ধরে যে উঠে এসেছিল স্টিল-লাইফ আঁকার রীতি, রান্নার বইয়ের খাদ্যসামগ্রীর চোখ-ধাঁধানো ছবি সেই স্টিল-লাইফেরই জনপ্রিয় পুনর্নির্মাণ। সাবেকি স্টিল-লাইফের তৈলচিত্র তাই যদি হয় নবাগত পুঁজিবাদের হাত ধরে আসা পণ্যপূজা বা কমোডিটি ফেটিসিজমের অন্যতম শৈল্পিক মূর্ত রূপক, খাদ্য আলোকচিত্র সেই ধারাটিকেই দান করল এক নতুনতর, জনপ্রিয় ব্যবসায়িক রূপ। বলা বাহুল্য, সঞ্জীব কাপুরের বই বা ‘হ্যাংলা’র ছবিগুলিও সেই পণ্য-প্রতীকতার হাত ধরে, সেই জটিল পণ্যায়নের রাজনীতিকেই আরও একবার পুনরুজ্জীবিত করল।
তবে কিনা, সেই পণ্যায়নের চাবিকাঠি আসলে কার হাতে, এ নিয়েও ওঠে প্রশ্ন। মানে, ‘মায়ের হাতের রান্না’ এবং তার পুনঃপুনঃ মহিমান্বিতকরণ যদি আসলে হয় একধরনের পুঁজি-বহির্ভূত, অব্যবসায়িক খাদ্য ও রন্ধনসংস্কৃতির খোঁজ, তা আর ঠিক এই সব বই, ছবি, পত্রিকার দৌলতে তেমনটি কিন্তু রইল না। বরং, পেশাদার শেফ পুত্রের হাত ধরে, ঘরোয়া সেই খাদ্যসংস্কৃতি পুনর্লিখিত, পুনর্নির্মিত হল। এবং, সেই পুনর্লিখন/ পুনর্নির্মানের হাত ধরে সেই ‘ঘরোয়া খানা’ পরিণত হল আপাদমস্তক, ব্যবসায়িক বিনিময়ের পণ্যে। যদিও, সেই ব্যবসায়িক বৈষয়িকতার ভরকেন্দ্র হয়ে উঠলেন না রান্না করা মায়েরা। তাঁরা রয়ে গেলেন ‘মা’ শব্দটির অনাম্নীতার আড়ালে, বিমূর্ত ছায়ামূর্তি হয়ে। অর্থাৎ, তাঁরা কেউই ঠিক ‘শেফ’ বা ‘রাঁধুনি’ হয়ে উঠলেন না। থেকে গেলেন ‘মা’ হিসেবে, যাঁর মাতৃত্বের হাজারও দায়িত্বের একটি হল সন্তানকে সুস্বাদু খাবার রেঁধে খাওয়ানো।
অবশ্য, প্যাকেটজাত খাদ্যশিল্পে ‘মা’ বিষয়টি একটি ব্র্যান্ড। অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্র্যান্ড। যেমন ধরুন, কেরালায় হেডকোয়ার্টার এমন একটি রেডিমেড ব্রান্ডের নাম ‘মাদার্স’। আছে আরেকটি ব্র্যান্ড ‘মাদার্স রেসিপি’ এবং তাদের হরেকরকম রেডিমেড আচার, মসলা মিক্স, ফ্রজেন খাবারের ছড়াছড়ি। বস্তুত, গোটা ভারত খুঁজলে ‘মমস কিচেন’ বা ‘মাদার্স কিচেন’ নামে পাওয়া যাবে হাজার হাজার ভোজনালয়। বা, মুখরোচক চানাচুরের এই কপিটা :
“মায়ের হাতের স্বাদ বরাবরই অতুলনীয়। এই যেমন চটজলদি কিছু স্ন্যাকসের কথাই ধরুন না। মায়েরা নিমেষেই এমন কিছু একটা বানিয়ে ফেলেন যা দুনিয়ার যে কোনও রেস্তোরাঁয় অমিল। এবার মায়ের হাতের মতোই ভালোবাসার স্বাদ ও আন্তরিকতা নিয়ে হাজির মুখরোচকের টিফিন স্নাক্স। প্রতিটি টিফিন স্ন্যাক্স প্রোডাক্ট তৈরি হয় ১০০% স্বাস্থ্যকর উপাদান ও স্বাদের মেলবন্ধন দিয়ে। যা খেলে মনে পড়ে যায় ছোটবেলার সেই মায়ের হাতের চিড়ে ভাজা, মুড়ি বা চাল ভাজার কথা।”
অবশ্যম্ভাবীভাবে, মা এখানে একটি নির্মাণ। যে নির্মাণের সাথে জড়িয়ে আছে এক ধরনের লিঙ্গায়িত গার্হস্থ্যের নির্মাণ প্রচেষ্টা। এবং, সেই গার্হস্থ্যতার রূপকল্পের কেন্দ্রে রয়েছে একটি সদাহাস্যময়, রন্ধনপটু মাতৃমূর্তি। মা’র বানানো খাবারের সঙ্গে আসে তাই এক ধরনের বিশুদ্ধ, পবিত্র, নির্ভেজাল গার্হস্থ্যের অনুরণন। তাই, একদিকে যেমন ‘মার হাতের রান্না’ বিষয়টি উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় একধরনের দ্বৈততা — সর্বজনীন, ব্যবসায়িক খাদ্যক্ষেত্রের সঙ্গে — তেমনি, এই লক্ষণাটির পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তৈরি হয় এক ধরনের বিশ্বাসযোগ্যতার বয়ানও। যে বিশ্বাসযোগ্যতাকে বিক্রয় করা যায়। অর্থাৎ, এই ‘মা; বা ‘মায়ের হাতের রান্নার’ জয়গানের পেছনে যদি থেকে থাকে একধরনের পুঁজি-বহির্ভূত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অনুসন্ধান, যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবেন মা বা মাতৃত্ব, তাহলে সেই পুঁজি-বহির্ভূত সাংস্কৃতিক ও আবেগজাত জগতের যে জনপ্রিয় চাহিদা, তাকেও পুঁজিবন্দি করা হল। বস্তুত, পুঁজিবন্দিত্ব এখানে কাজ করে একাধিক স্তরে।
মানে, অন্দরমহল বা গার্হস্থ্যতা বা শেষত মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্যতা—পুঁজির নিয়মে চলে না, এ কথা বলা বা মনে করা পাগলের প্রলাপমাত্র। একটু ভেবে দেখুন, অন্দরমহলেও পণ্য সামগ্রীর ব্যবহার হয়, রান্নাঘরের নিত্যনৈমিত্তিক জিনিস আসে বাজার থেকে, এবং সর্বোপরি, অন্দরমহলের এই পণ্যজগৎকে বাঁচিয়ে রাখতে খরচ হয় প্রচুর, প্রচুর অর্থনৈতিক শ্রম, বিনিয়োগ করা হয় সার্বিকভাবে কোটি কোটি টাকা। তৎসত্ত্বেও, অন্দরমহলের সমস্ত সম্পর্ক পুঁজির কঠোর ও সংকীর্ণ নিয়মে চালিত হয় না। সেই পুঁজি-বহির্ভূততার মধ্যে আছে সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার সম্পর্ক, অন্যান্য রক্তিয়তা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক। এবং, সর্বোপরি, যে লিঙ্গায়িত শ্রম বিভাজনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে পরিবার, এবং অন্দরমহল—অর্থাৎ, পরিবারের মেয়েদের/ মায়েদের বিনামূল্যের গৃহশ্রম—তা যেন কোথাও একটা গার্হস্থ্যতা, অন্দরমহল ও তার সঙ্গে পুঁজির সম্পর্ককে করে তোলে জটিল থেকে জটিলতর।
তো, ‘মায়েদের হাতের রান্না’—তা সে চটপটে মুখরোচক পকোড়াই হোক, অথবা বিস্তারিত পঞ্চব্যঞ্জন—তা সেই বিনামূল্যের শ্রমের ধারাবাহিকতারই ফসল। যদিও, সেই ‘মায়ের হাতের রান্না’—বিনা পারিশ্রমিকের শ্রমফসল—তাও আসলে পণ্য সম্পর্কের বাইরে অবস্থিত নয়। বরং, বলা যেতে পারে, ‘মায়ের হাতের রান্না’-র মধ্য দিয়ে, বাজার থেকে কেনা খাদ্যপণ্য আহার্যে পরিণত হয়। কাজেই, আবারও, পণ্য ও পণ্যায়ন-বহির্ভূত সম্পর্কের হিসাব এখানে জটিল। সেই জটিলতার ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই এই জাতীয় শ্রমকে মূলধারার অর্থনীতিতে বলা হত ‘লেবার অফ লাভ’, এবং, যেহেতু, ‘লেবার অফ লাভ’, বা ভালোবাসা নিঃসৃত শ্রম, যার কোনও বাজারি মূল্য নির্ধরণ করা যায় না, তাই এ জাতীয় শ্রমকে সাধারণ ভাবে রাখা হয়েছিল মূলধারার অর্থনৈতিক সম্পর্কের বাইরে। এবং, যে জাতীয় শ্রমকে ভাঙাচোরা, আংশিক ভাবে হলেও, অর্থনীতির আওতায় আনতে, পুঁজিবাদের মূল দ্বন্দ্বগুলির আওতায় আনতে মার্ক্সবাদী, নারীবাদী তাত্ত্বিক ও কর্মীদের কালঘাম ছোটাতে হয়েছে। ‘মায়ের হাতের রান্না’-র সঙ্গে সঙ্গে বিনামূল্যে প্রাপ্ত যে হাসিমুখ, তার সমাজতাত্ত্বিক- রাজনৈতিক অভিঘাত বুঝতে ও তত্ত্বায়িত করতে গিয়ে ‘ইমোশনাল লেবার’ বা ‘আবেগজাত শ্রম’-এর ধারণার অবতারণা করতে হয়েছে।
কিন্তু, সমকালীন খাদ্যবিষয়ক লেখালেখি ও গণমাধ্যমজাত উপস্থাপনায় যা দেখা গেল, তা হল, এই যে, গত কয়েক দশকের এই মর্মে যে রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক কাজ, তার প্রমাণ মোটামুটি লুপ্ত। তার বদলে, কখনও হেঁশেলে মায়েদের সৃষ্টিশীলতার নামে, কখনও মায়েদের অন্তহীন ভালোবাসার নামে, উধাও করে দেওয়া হল অন্দরমহলের গার্হস্থ্য হেঁশেলে মেয়েদের সমস্ত শ্রমচিহ্ন। বকলমে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার হাজির করা হল ‘লেবার অফ লাভ’ তত্ত্ব, এবং সেই উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে মেয়েদের/ মায়েদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল রন্ধনশ্রমজাত প্রায় সমস্ত বৈষিয়কতাও। অতএব, রান্নার, রান্নার রেসিপির সংকলন, ‘মায়ের হাতের রান্না’-র উদযাপন তথা মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির আড়ম্বরপূর্ণতার মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত করা হল অন্দরমহলের বিনামূল্যের শ্রমের নিরন্তর চক্করকে। এবং, তা করা হল সেই বিনামূল্যের শ্রমের পণ্যায়িত সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে।
অবশ্য, এই যে ‘মায়ের হাতের রান্না’-র মা, সেখানে অবশ্য ঠিক যে কোনও মা হলেই হবে না। ‘হ্যাংলা’-র পাতায় তাই আঁকা হল এক আদর্শ মাতৃত্বের দৃশ্যপটও। কেমন সেই চিত্র? ২০১৪ সালের মাদার্স ডে বিশেষ সংখ্যা “তোমার ছায়ায়, তোমার মায়ায়” শিরোনামে যে প্রচ্ছদ নিবন্ধ, সেখানে লেখা হল—মায়ের হাতের রান্না’— ব্যাপারটার মধ্যেই যে মিশে আছে আলাদা স্বাদ ও মিষ্টি গন্ধ। আর হবে নাই বা কেন? স্নেহ, প্রশ্রয়, ভালবাসা ও মমতা দিয়ে মোড়া যে এই রান্না! এ রান্নার কি কোনো তুলনা চলে? আজ হারিয়ে যাওয়া মায়েদের রান্নার কথা লিখতে গিয়ে একটা ছবি বারবার চোখে ভেসে ওঠে—আটপৌরে শাড়ি পরিহিতা, কপালে ও সিঁথিতে তকতকে সিঁদুর, খোঁপায় ঘোমটা টানা আর উনুনের পাশে বসে রান্না করছেন মা। সারাদিন ধরে চলতো হেঁশেলে কতো রান্না। ডাল, সবজি, মাছ, মাংসের পাশাপাশি খোসা, নানারকম বীজ, পাতা, ফুল, ফল, মাছের কাঁটা—কিছুই যে ফেলা হতো না একান্নবর্তীর রান্নাঘরে। সে-সব রান্নার স্বাদ বড় বড় রেস্তোরাঁকেও হার মানিয়ে দেবে অনায়াসে। অথচ ছিল না রকমারি মশলার আদিখ্যেতা, সাজানোর বাহার। যুগের হাওয়ায় হারিয়ে গেছে সে-সব অনেক বাঙালি রান্নাই।”
ভালোবাসা, মমতা ইত্যাদি দিয়ে মোড়া ‘মায়ের হাতের রান্না’-র দুই ধরনের চরিত্রায়ণ করা হল তাহলে এইখানে। সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও। মা এখানে প্রাচুর্যময় এক পরিবারের গৃহিণী। এবং, সরাসরিভাবে, প্রত্যক্ষ শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অভিহিত না করলেও, সে প্রাচুর্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জমিদারবাড়ির ছায়া। কাজেই, শুধু মা নন, বাঙালি রান্নার সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল উচ্চবর্ণীয় হিন্দু নারীত্বের একটি প্রতিলিপি ও বয়ানও। সে বয়ানে সারাদিন হেঁশেল ঠেললেও ঘামে ধেবড়ে যায় না মার কপালের সিঁদুরের টিপ্, ঘামে জবজব করে না গাল, গলা, হাত; লাল হয়ে ওঠে না চোখ, দপদপ করে না মাথার দু’পাশের রগ। অর্থাৎ, আবারও, এই যে রন্ধনরতা মায়ের একটি আদর্শকল্প গঠন করা হল, সেখানে রইল না কোনও শ্রমচিহ্ন। বিনামূল্যে শ্রমের স্বীকৃতি তো দূরের কথা, হেঁশেলের যে জমজমাট কার্যক্রমের কথা বর্ণনা করা হল, সেখানে কোনও ধরনের কোনও শ্রমেরই পদচারণার কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হল না।
এবং, তার সঙ্গে যেটা লক্ষ্যণীয় বিষয়, সেটা হল, এই দৃশ্যপটটি তৈরি করা হল এমন সময়ে যখন মধ্যবিত্ত মেয়েদের একটি অংশ আর ঠিক সেইভাবে রান্নাঘর আবদ্ধ নন। বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক জীবনে একটি বড়ো পরিবর্তন এসেছে মেয়েদের কাজে বেরোনো এবং সর্বজনীন জগতে তাঁদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। অন্যভাবে দেখতে গেলে, মেয়েদের সৃষ্টিশীলতার ধারণাও, আজ আর রান্নাঘর ও রন্ধনপটীয়সীতায় সীমাবদ্ধ নয়। কাজেই, প্রশ্ন ওঠে, কোথাও কি এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক স্মৃতিমেদুরতা, বা ফিউডাল নস্টালজিয়ার মধ্য দিয়ে ‘মায়ের হাতের রান্না’-র সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তি কি এক ধরনের সার্বিক পিতৃতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াই নয়? অনেকটা যাকে মার্কিনী নারীবাদী সাংবাদিক সুসান ফালুদি ‘বাকল্যাশ’ বলে বর্ণনা করেছিলেন? এবং, যে পিতৃতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া ও নষ্টালজিয়াকে পাথেয় করে পুঁজিনির্ভর সংস্কৃতি শিল্প বা কালচার ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলে তার সাংস্কৃতিক গণউৎপাদনজাত উপস্থাপনাসমূহ?
অবশ্য, বাংলার মেয়েদের যে সুদীর্ঘ ও জটিল ইতিহাস, সেখানে বিধৃত হল জমিদারি রান্নাঘরের একটি বিকল্প প্রাত্যহিকতার চিত্র। যেমন, সুলেখা সান্যাল ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘নবাঙ্কুর’ উপন্যাসে জমিদার বাড়ির অন্দরমহলের একটি ভিন্নতর রূপায়ণ হাজির করলেন। কী লিখেছিলেন সেখানে সুলেখা তাঁর কিশোরী নায়িকা ছবির দৃষ্টিকোণ থেকে?
“মাকে দেখতো রান্নাঘর থেকে ক্লান্ত মুখে বেরিয়ে এসে উনুনে হাওয়া দেবার ভাঙা পাখাখানা নিয়ে হাওয়া খেতে, কাছে দাঁড়ালেই বলতো, সরে যা ছবু, হাওয়া ছাড়।
— নয়তো বলতো, কটা ঘামাচি মেরে দিবি?
“সে মা’র ঘামাচি ভরা পিঠ দেখে শিউরে উঠলে মমতা বলতেন, কী করবো ? সারাদিন রান্নাঘরে আগুনের আঁচে থাকি—দেখিসনে?
“কেন থাক সারাদিন?
“মমতা তখন হাসতেন, ঘরে ঘরেই তো এই মেয়েদের বিধিলিপি—বড়ো হ বুঝবি। …তোর ঠাকুমার কথা জানিস? ন’ বছরের গৌরীদান করা মেয়ে। শ্বশুরবাড়িতে অতটুকু মেয়েকে বড়ো বড়ো হাঁড়ি-কড়াই নিয়ে রান্না করতে হতো। কতদিন নাকি ভাতের হাঁড়ি পায়ের ওপর পড়েছে, জোরে কাঁদবার পর্যন্ত উপায় ছিল না—বউ যে।”
বলার অপেক্ষা রাখে না, জমিদারি বাড়ির অন্দরমহলের হেঁশেলের এক টুকরো ছবি তুলে ধরলেন এখানে সুলেখা। সেই ছবিতে নেই কোনও জিভে জল আনা খাবারের বর্ণনা, নেই কোনও সুস্বাদু খাবারের লম্বা তালিকা। অর্থাৎ পাঠকের রসনা পরিতৃপ্ত করার কোনও প্রচেষ্টা এখানে করেননি সুলেখা। তার বদলে আছে রান্নাঘরের ভেতরে মেয়েদের, মায়েদের শ্রমের খতিয়ান। যে শ্রম সুলেখার লেখনীতে দেখা দেয় গভীর সামাজিক হিংসা হিসেবে। প্রাত্যহিক হিংসা হিসেবে। যে প্রাত্যহিক, সামাজিক হিংসা বদলে দেয় মেয়েদের, মায়েদের শরীর। রান্নাঘর ও তদ্জনিত শ্রম এখানে, সুলেখার কলমে, দেখা দেয় মেয়েদের শারীরিক যন্ত্রণা হিসেবে।
সুলেখার লেখনী ও সমসাময়িক খাদ্যসাহিত্যকে যদি পাশাপাশি রাখি তাহলে দেখব এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। সুলেখার লেখায় রান্নাঘর আসলো সামাজিক হিংসার ক্ষেত্র হয়ে, সমসাময়িক খাদ্যসাহিত্যে ঠিক তার বিপরীত—এক ধরনের গার্হস্থ্যতাকেন্দ্রিক রোমান্টিকতার ধারকবাহক হয়ে। ‘নবাঙ্কুর’ লেখা হওয়ার প্রায় ষাট বছর বাদে সমসাময়িক খাদ্য-গণমাধ্যম ও লেখালেখিতে যে ধরনের শ্রম-বিযুক্ত খাদ্য, থুড়ি, পণ্যপূজার নমুনা দেখা যায়, যার মধ্য দিয়ে বিপুলভাবে মহিমান্বিতও করা হয় গার্হস্থ্য শ্রমের লিঙ্গায়িত বিভাজনকেও, তার মধ্য দিয়ে সর্বজনীনক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবিত করা হল এক ধরনের অনৈতিহাসিক, অপার্থিব মাতৃত্বকে। সেই সমস্ত রূপায়ণের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, সমসাময়িক খাদ্যসাহিত্য কি তবে এক ভাবে হয়ে উঠছে আমাদের ক্রমশ পিছোতে থাকা সময়েরই প্রতিভূ? যেখানে, বকলমে হৃত খাদ্যবস্তুর নাম করে তৈরি হয় ‘রান্নাঘরই মেয়েদের প্রধান জায়গা’ জাতীয় মতাদর্শগত বলয়? এবং, সেই বলয়ের কেন্দ্রে থাকে এক ধরনের পণ্যায়িত মাতৃত্ব-বন্দনা? এর বিপরীতে, অন্যধরনের খাদ্য-সাহিত্য বা গণমাধ্যমের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে গেলে ঠিক কি ধরনের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক শ্রম দিতে হবে আমাদের?
মানে, রান্নাঘরে ঘেমেনেয়ে আমাদের সবার জন্য খাদ্যশ্রম দেয় যে মা, তার মুখে সবসময়ে হাসি লেগে থাকে না যে। বরং থাকে চিল-চিৎকার, খিস্তিখাস্তা, বাসনকোসনের ঝনঝনাতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জিহ্বা চালনা। সাবেকি বহু বাড়ির যে স্থাপত্যপরিকাঠামো, সেখানে রান্নাঘরটার অবস্থান বাড়ির এক কোণে, ধোঁয়া-তেল-ঝাঁঝ মিলিয়ে বড়োই অস্বাস্থ্যকর সেই জায়গা। এর পর থাকে বাড়ির মেয়েদের রান্নাঘরের দখল নিয়ে পারস্পরিক লড়াই, রান্নাঘরকে কেন্দ্র করে একে অন্যের উপর আধিপত্য। থাকে বাড়ির বাইরে থেকে কাজ করতে আসা গৃহশ্রমিক। অর্থাৎ, রান্নাঘর একটি জটিল উৎপাদনস্থল, যা কিনা চলে নিজস্ব উৎপাদনসম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে। আবার, এই জটিল উৎপাদনসম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়েই তৈরি হয় অসাধারণ সমস্ত সৃষ্টি, যাকে শিল্প বলে অভিহিত না করলে বাদ থেকে যাবে এই পৃথিবীর একটি বৃহৎ প্রাত্যহিক নৈপুণ্যের ইতিহাস। এই সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে যদি লেখা হয় ‘মায়ের হাতের রান্নার’ বিবরণ, সেই খাদ্যদ্রব্যের চটকদারি ছবি, তবে তো আসলে তৈরি করা হয় একটি খণ্ডচিত্র। যে খণ্ডচিত্রের চরিত্র আসলে ঘোরতরভাবে মতাদর্শগত। তাই, আজ প্রয়োজন এক ধরনের জটিল বস্তুবাদী খাদ্যসাহিত্যের, যেখানে এই রন্ধনজাত সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে এই ততোটা আকর্ষণীয় নয়, এমন বাস্তবতার বিবরণও। একমাত্র, সেই জাতীয় লেখনীর মধ্য দিয়েই আমাদের খাদ্য-সংস্কৃতির তুলনামূলক সম্যক মূল্যায়ণ সম্ভব।
লেখক কবি ও সাহিত্যের অধ্যাপক।

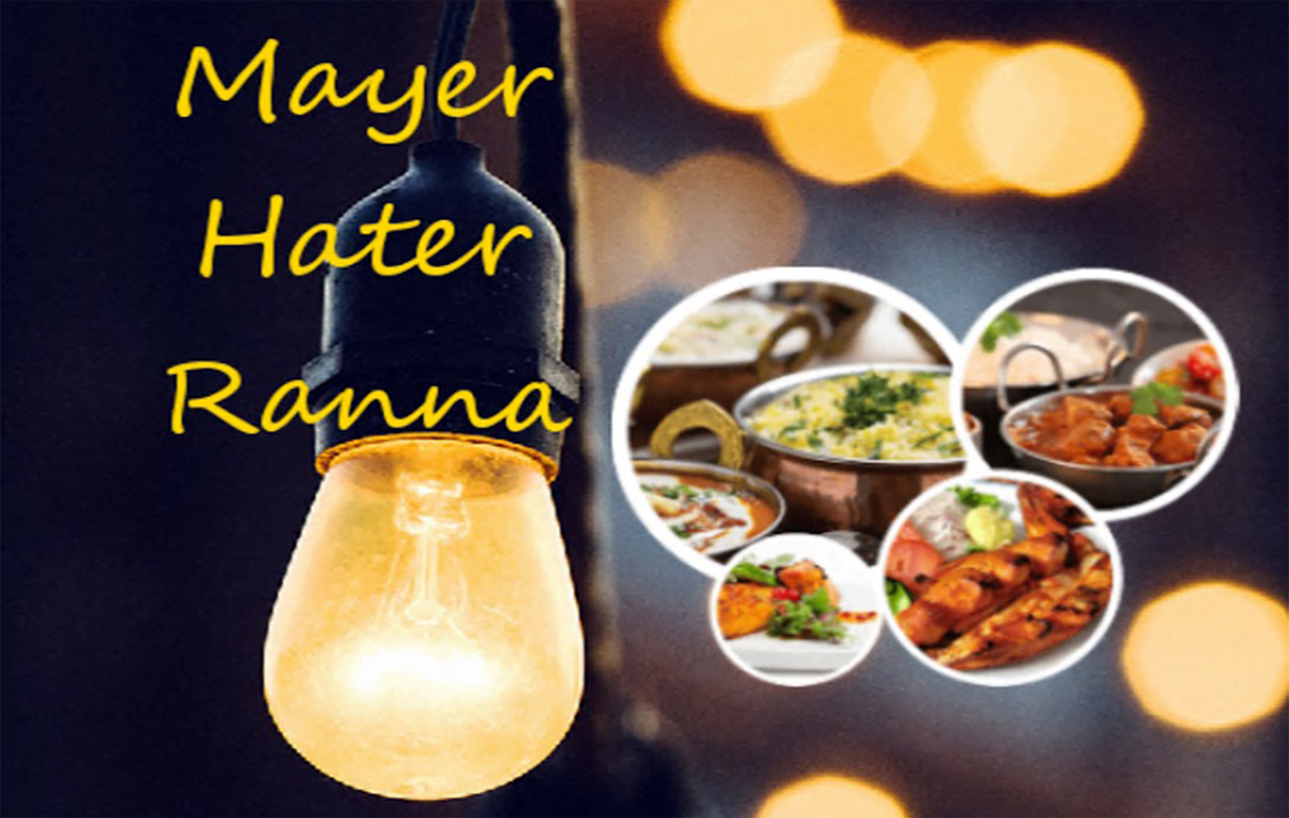
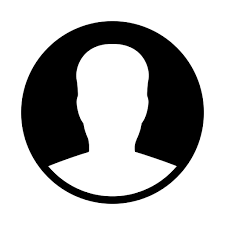
yes , a good work done .