বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি আর বজ্রকঠিন চরিত্রের কল্পকথাগুলি একটু একটু করে ধুলো হয়ে উবে যাচ্ছে অনেকদিন হল। এখন তর্কটা এসে দাঁড়িয়েছে তিনি আদৌ এদেশের – দেশের মানুষের – জন্য শুভ কিছু, কল্যাণকর কিছু করে – বা অন্তত শুরু করে – যেতে পেরেছিলেন কি? নাকি স্রেফ ব্রিটিশ প্রভুদের ইশারায়, অঙ্গুলিহেলনেই বাঁধা ছিল তাঁর কার্যপরম্পরা? ঘুলিয়ে ওঠা কাদাজল সামান্য স্বচ্ছ করার প্রচেষ্টায় অশোক মুখোপাধ্যায়। এটি ষষ্ঠ ও শেষ পর্ব। প্রথম , দ্বিতীয়,তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্ব ক্রমান্বয়ে এখান থেকে পড়া যাবে – লিংক এক, দুই , তিন, চার ও পাঁচ। প্রথম চারটি পর্ব ফেসবুকে লিখিত নিবন্ধের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ ছিল। পঞ্চম ও শেষ পর্ব লেখকের নতুন সংযোজন।
[১১]
পরিশেষে ঘোষ ও অন্যান্যদের বিপ্লব বিলাসিতার আর একটা চমকপ্রদ উদাহরণ এবার তুলে ধরব। বিদ্যাসাগরের একেবারে শেষ জীবনে সহবাস সম্মতি আইন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তৈরি করা অপপ্রচার। হ্যাঁ, এবার আর ভুল নয়, একেবারে সত্যিকারের অর্থে অপপ্রচার। একটা স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্য অত্যন্ত সচেতন ভাবে ভুল বা অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার বাজে চেষ্টা।
এবং কারা সেটা করেছেন? বিনয় ঘোষ, অশোক সেন, স্বপন বসু, প্রমুখ। এই দ্বিতীয়/তৃতীয় নামগুলি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বিনয় ঘোষের পূর্বকথিত মিথ্যাচার সম্পর্কে অমল ঘোষ সবিস্তারে লেখার পরেও এবং বিদ্যাসাগরের মূল পত্রটি হাতে পাওয়া সত্ত্বেও এঁরা কীভাবে সেই একই অভিযোগ আবার নতুন করে আনতে পারলেন—সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যও অনেক দিন ধরেই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে নানা রকম“প্রগতিশীল” বিভ্রান্তির স্বরূপ উন্মোচন করে অনেক জায়গাতেই লিখেছেন। সেগুলো এনাদের না জানার কথা নয়। না জেনে থাকলে, তাও যথেষ্ট বিস্ময়প্রদায়ক!
অতএব প্রশ্ন না জেগে পারে না, এরকম করার পেছনে কোথাও কি কোনো আবশ্যিক বাধ্যতা কাজ করছে?
মূল ঘটনায় প্রবেশ করা যাক। ১৮৯১ সালের গোড়ার দিকে বাল্য বিবাহের কারণে অল্প বয়সী নারীদের উপর স্বামীর শারীরিক অধিকারের ফলস্বরূপ যে এক ধরনের বলাৎকার ঘটত, এবং অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হত, তাকে আটকানোর জন্য ইংরেজ সরকার Consent Bill বা সহবাস সম্মতি বিল এনে একটা আইনি রক্ষাকবচ তৈরি করার কথা ভাবেন (ইংলন্ডে ১৮৯০ সালে অনুরূপ একটি আইন চালু হয়)। তাতে সহবাসের বয়স প্রচলিত দশ থেকে বাড়িয়ে বারো বছর করার প্রস্তাব ছিল। (আরও অনেকের মতো) বিদ্যাসাগরের কাছে তারা বিলটির খসড়া কপি পাঠিয়ে জানতে চায়, এর সাথে হিন্দুদের ধর্মীয় কোনো প্রথার বা শাস্ত্রীয় কোনো নির্দেশের বিরোধ হবে কিনা।
বিদ্যাসাগর প্রস্তাবিত বিলের সেই বয়ানে আপত্তি জানিয়ে সরকারের কাছে এক পত্রে লেখেন, বয়স নির্দিষ্ট করার বদলে “I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child wives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real and more extensive protection than the Bill.” [বক্রাক্ষর আমাদের আরোপিত; মূল পত্রে কোনো বক্রাক্ষর নেই বা থাকার প্রশ্নও ছিল না।]
ব্যস, হয়ে গেল। শুধু মাত্র এই (বক্রাকৃত) শব্দযুগলকে পাকড়ে নিয়ে বিনয় ঘোষ লিখে ফেললেন, বিদ্যাসাগর নাকি এই “ধর্মীয় রীতি” কথাটির উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করেছেন, বহুবিবাহের বিরোধিতা করেছেন। তাহলে কেন এই শাস্ত্রকথার আড়ালে বাল্যবিবাহের একটি নিরোধক আইনের প্রস্তাবে আপত্তি করতে গেলেন? “এ কি তাঁর বার্ধক্যের দুর্বলতা ও মানসিক দ্বন্দ্ব?”
প্রথমেই আমরা অবাক হয়ে ভাবি, বিনয়বাবু কোথায় দেখলেন, বিদ্যাসাগর “ধর্মীয় প্রথা”-র উপর জোর দিয়েছেন? তিনি বলছেন, আইনে এমন এক ব্যবস্থা করা হোক যা নারীদের পক্ষে যথেষ্ট রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করবে, অন্য দিকে তা ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সাঙ্ঘর্ষিক না হওয়ায় কারোও পক্ষে মানতে অসুবিধা হবে না বা অজুহাত দেওয়া সম্ভব হবে না। আলাদা করে না বললেও, জোর যদি তিনি দিয়ে থাকেন কোথাও, তা এই রক্ষাকবচ নির্ধারণের প্রশ্নের উপর।
দুনম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, একটা প্রস্তাবিত আইনের বিবদমান বয়ানে আপত্তি জানানো এবং বিকল্প পরামর্শ প্রদান মানে কি সেই আইন রচনায় আপত্তি জানানো? বিনয় ঘোষের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তি এই দুই বিষয়ের মধ্যে যে কিঞ্চিত পার্থক্য আছে তা জানেন না ভাবতে হলে বরং তাঁকেই সেই সময় বার্ধক্যজনিত ব্যাধি জরাগ্রস্ত করছিল কিনা খোঁজ নিতে হয়!
তৃতীয়ত, এই বিলের আলোচ্য বিষয় ছিল বিবাহিতা নারীর সঙ্গে তার স্বামীর প্রথম শারীরিক সংসর্গের বয়ঃক্রম নির্ধারণ বা পরিবর্তন। এর সঙ্গে বাল্যবিবাহ নিরোধের প্রসঙ্গ কোত্থেকে এল? সহবাস সম্মতির বয়স বারো হলেই বাল্যবিবাহ দূর হয়ে যেত—বিনয়বাবুরা সত্যিই একথা বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগরের “সীমাবদ্ধতা” দেখাতে হবে বলেই বোধ হয় তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে কথাটা পেড়ে এনেছিলেন!
চতুর্থত, বিদ্যাসাগর বয়স উল্লেখের পরিবর্তে একটা শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য (নারীর বয়ঃপ্রাপ্তি কালে মাসিক ঋতুর আবির্ভাব)-কে নিষেধের মানদণ্ড করতে চেয়েছেন, এবং বলেছেন, তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী, যাদের ক্ষেত্রে তের, চোদ্দ বা পনের বছর বয়সে এই বৈশিষ্ট্য প্রকট হবে, তাদের সঙ্গে সেই সেই বয়সের আগে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা স্বামীদের ক্ষেত্রে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে বলে ব্যবস্থা রাখা হোক। বারো বছরকে নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থাতে আপত্তি জানানোতে কি তাহলে বাল্যবিবাহের পক্ষে বলা হল? নাকি, সরকার প্রস্তাবিত বিলের তুলনায় তৎকালীন বালিকা বধূদের জন্য অনেক বেশি বাস্তবসম্মত এবং ব্যাপকতর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হল? বিনয় ঘোষ ইংরেজি জানেন না, পত্রটি পাঠ করে তার বয়ানের মর্মার্থ বুঝতে পারেননি—এমনটা কি আদৌ হতে পারে? নাকি সমস্তটা জেনে শুনেই, তাঁর ১৯৬৮-উত্তর নব অর্জিত “শ্রেণিগত” উপলব্ধির সঙ্গে জবরদস্তি মেলাতে গিয়ে এই সামান্য(?) চালাকিটুকুর আশ্রয় নিয়ে ফেললেন?
সর্বশেষে, আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বিনয় ঘোষ সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর নতুন উপলব্ধির আলোকে (বা আসলে অন্ধকারে) অগ্রাহ্য করে গেছেন। ওই পত্রেই বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রেও স্ত্রীর প্রথম ঋতুর আগে স্বামীর শারীরিক সংসর্গ স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু এই নির্দেশ অমান্য করলে যে শাস্ত্রীয় শাস্তি বরাদ্দ রয়েছে তা হচ্ছে “আধ্যাত্মিক ধরনের”। একদিন আধ পেট খেয়ে থাকা বা একশ বার গৃহদেবতার নাম জপা জাতীয় নানা রকম কঠোর(?) নির্দেশিকা। বুদ্ধিমান লোকেরা সহজেই তাকে পাত্তা না দিয়ে স্বেচ্ছাচার চালাতে পারে। কিন্তু একে একবার আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করলে তাদের আর সেই সুযোগও থাকবে না। অর্থাৎ, আলোচ্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অলিখিত যুক্তিটি হচ্ছে এরকম: আইনটি প্রবর্তিত হওয়ার পর ধর্ম বা শাস্ত্র মেনে চল তো কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বাপু, ধর্মের কল বাতাসে নড়ুক আর না নড়ুক, ব্রিটিশের আইনের কল কিন্তু নজর রাখবে তোমার উপর। যা করতে চাও বুঝেসুজে কোরো। আইনটি ভাঙতে গিয়ে “ধর্মীয় প্রথা”-র অজুহস্তটি কিন্তু আর তুমি ব্যবহার করতে পারছ না। এর নাম যে “ধর্মীয় রীতি”-কে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া, তা একমাত্র একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিদ্র-সন্ধানীর পক্ষেই বলা সম্ভব!
গোটা পত্রটি এইভাবে না পড়ে, না দেখে, দুটো পছন্দসই শব্দকে হাতে নিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে আপন মনের মাধুরী, থুড়ি, অসূয়া, মিশিয়ে এই যে অনৃত বাচনটি বিনয় ঘোষ একবার তৈরি করে ফেললেন, বিভিন্ন উৎস গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের গোটা পত্রটি প্রাপ্তব্য হওয়া সত্ত্বেও একের পর এক স্বপন বসু, অশোক সেন, প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা সেই মিথ্যা অভিযোগটাকে বেশ কয়েক দশক ধরে পর পর বাঁচিয়ে রাখলেন।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য মনে করেন, বিনয় ঘোষের এই ভ্রান্তির কারণ তিনি সুবল চন্দ্র মিত্র এবং বিহারীলাল সরকারের রচিত বিদ্যাসাগর জীবনী দুটিতে প্রদত্ত এই বিষয়ক খণ্ডিত উদ্ধৃতি দেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আর পরবর্তী বিদ্বানেরা বিনয় ঘোষের কথার উপর নিশ্চিন্ত নির্ভর করতে গিয়ে ভুল করে গেছেন। এই ধারণা সত্য কিনা বলতে পারব না। যদি সত্য হয় তাহলে ১৯৬০-এর দশকে আমি যে বিনয় ঘোষকে জানতাম, তাঁর সম্পর্কে সমস্ত পুরনো ধারণাই বদলে ফেলতে হবে। বিদ্যাসাগর বিষয়ে বিচার করার যোগ্যতাই তাঁর থাকবে কিনা তখন সন্দেহ করতে শুরু করব।
তবে, আমার অনুমান অন্য রকম। তাঁরা সকলেই স্রেফ একটা ভ্রান্ত বিচারধারাকে সচল করে রাখার জন্য খুব সচেতন ভাবে এই কাণ্ড করে গিয়েছেন। আসল তথ্য খোঁজার কোনো তাগিদই অনুভব করেননি।
হ্যাঁ, এই শেষ কথাটায় একটু জোর দিতে চাইছি।
অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও, সামাজিক সামষ্টিক কোনো প্রশ্নে ভুল চিন্তা দিয়ে একবার শুরু করলে, তাকে সময়মতো শুধরে না নিলে, তা নিয়েই গল্প গুজব গান বাজনা চালিয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে উত্থিত সমালোচনাকে গ্রাহ্য না করলে, এক সময় আর শুধু সেই অগোচর ভ্রান্তির মধ্যে অবগাহনেই মানুষের বৌদ্ধিক আচরণ সীমিত থাকে না, সেই বিভ্রান্তিকে জীবিত রাখা এবং সঞ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে মিথ্যা বচন নির্মাণের দিকেও গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে যেতে হয়। তখন তা শেষ পর্যন্ত এক অনৈতিক আচরণে পরিণত হয়। বিনয় ঘোষ বা অশোক সেন প্রমুখ বিদ্বজ্জনদের ক্ষেত্রে এরকম বাক্য বিন্যাস গঠন করতে খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের যে উপায় নেই!
তাঁদের এই ভ্রান্ত বিচার থেকে মিথ্যা অভিযোগ বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে ব্যক্ত হলেও আসলে এর সূত্রপাত হয়েছিল এক “মুৎসুদ্দি” তত্ত্ব থেকে শুরু করে বাংলার রেনেশাঁসকে সর্বপ্রযত্নে অস্বীকার করতে গিয়ে। অনেক প্রতিক্রিয়া, অনেক পিছুটান, অনেক রকম ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি ও অনেক কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়েও উনিশ শতকের একটা প্রায় একশ বছরের যে গৌরবময় অধ্যায়, তাকে গায়ের জোরে মুছে দিতে গিয়ে, দেশের বাস্তব পরিস্থিতিকে বিপ্লবের এক ভ্রান্ত রাজনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে, তাঁদের এই রাস্তায় পা ফেলতে হয়েছিল। স্বভাবতই তাঁরা একটা জিনিস মেলাতে পারছেন তো আরও পাঁচটা বিষয় মেলানো যাচ্ছে না! তখন আর উপায় কী? তাই সরোজ দত্তকেও যেমন খুব কাঁচা মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতে হয়েছে, বিনয় ঘোষ প্রমুখকেও একটু পাণ্ডিত্যের আবরণে সাজিয়েগুছিয়ে মিথ্যা অভিযোগ আনতে হল!
আমরা আশা করব, তাঁদের অনুসারী উত্তরকালের লেখকরা অন্তত এই সব কৃষ্ণ উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে চলার পথটা বদলে নেবেন!
পরিশেষে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা খুব জোর দিয়ে বলা দরকার।
বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনে দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর কলকাতা ছেড়ে সুদুর (অধুনা ঝাড়খণ্ডের) কার্মাটাঁড়ে গিয়ে বসবাস করার কারণে অনেকেই ধরে নিয়েছেন, তিনি হতাশা জনিত ক্লান্তি থেকে বার্ধক্যের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের তরফে অন্যায় অনৈতিক আচরণের ফলে বিতৃষ্ণা যে তাঁর জন্মেছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই কারণেই সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অন্যান্য কর্মসূচি থেকে, বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ রোধের প্রয়াস থেকে, নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই “হতাশা” “ক্লান্তি” ইত্যাদির ধারণা সর্বৈব ভুল। বার্ধক্য ও নিস্পৃহা (cynicism) তাঁকে কখনই গ্রাস করতে পারেনি। কর্তব্যের কর্মচাঞ্চল্য থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। বাংলাদেশের স্কুলগুলির উপর অভিভাবক সুলভ নজরদারি তিনি চালিয়ে গেছেন নিরন্তর। নিজের স্থাপিত স্কুল-কলেজ দুটিরও ভালোমন্দ নিয়মিত দেখভাল করেছেন সরাসরি। শুধু তো নরেন দত্তকে নয়, নিজের জামাতাকেও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি স্কুলের অর্থ ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করছিলেন বলে। বৃদ্ধ বয়সেই “অতি অল্প হইল”, “আবার অতি অল্প হইল”, “ব্রজবিলাস”, “রত্নপরীক্ষা”, ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রসঋদ্ধ কৌতুক পুস্তিকাগুলি রচনা করেছেন। পুরনো বইগুলির নতুন সংস্করণ বের করেছেন। বিভিন্ন সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ করেছেন।
মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস আগেও যেভাবে তিনি এই সহবাস সম্মতি বিলের উপর আলোচনা করেছেন, নানা শাস্ত্র ঘেঁটে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যুক্তিপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায়, তাঁর শরীর এবং মগজ তখনও কতখানি সক্রিয় ছিল। ধর্মীয় তথা শাস্ত্রীয় প্রশ্নটিকে সামনে এনে (আইনটি প্রচলিত হলে) যেভাবে তিনি তার ডানা ছেঁটে দিতে চেয়েছিলেন, তাতেও তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধি, রসবোধ এবং অজ্ঞেয়বাদী মননের অক্ষর সাক্ষ্য রেখে গেলেন। তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, তাঁরই লেখা “বর্ণপরিচয়” পাঠ থেকে যে উত্তর প্রজন্মের বর্ণ পরিচয় শুরু হয় আজও, তাঁরা আজও সেই বর্ণ পরিচয়ের গণ্ডী থেকে আর দু-এক পা-ও এগোতে পারেন না, জাজ্জ্বল্যমান সত্যকে চোখের সামনে দেখেও যেন দেখতে পান না!
আসল বিদ্যাসাগর তাই আজও অনেকের কাছেই অধরা। ধূপ আর কোপের আড়ালে।
[১২]
বোর্ডে একটা সরল রেখা আঁকা রয়েছে। না মুছে সেটাকে কীভাবে ছোট করে দেওয়া যায়? আইনস্টাইনের নামে প্রচলিত এই ধাঁধাটির উত্তর অনেকেই বোধ করি জানেন—নীচে চক দিয়ে একটা একটু বড় সরল রেখা এঁকে দিলেই আগেরটা ছোট দেখাবে। আইনস্টাইন এটা সত্যিই বলেছেন কিনা এখানে বড় কথা নয়। রেখাটিকে বড় করে দেখানোর জন্য অনুরূপে নীচে একটা ছোট সরল রেখা আঁকলেও হয়। আমাদের জন্য এই গল্পের নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে, বিদ্যাসাগরকে ছোট করতে হলে, তাঁর চেয়ে বড় একটা চরিত্র লাগবে। বিকল্পে, বুঝতে পারতে হবে, বিদ্যাসাগর যেখানে নেই সেখানে সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থাটা ঠিক কেমন?
দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সেটা বোঝার কিছু সুযোগ ঘটেছিল। তাঁকে নিয়ে ই-মাধ্যমে ছড়িয়ে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস জুড়ে বেশ কিছু তর্ক বিতর্ক আলোচনা করে ফেলেছি। তাতে আমার পরিচিতদের মধ্যে কেউ হয়ত খুশি হয়েছেন, অনেকে আবার বোধ হয় অখুশি। এখানে অনেক যুক্তিতর্ক তো হল। এবার খানিক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দিয়েই বিদ্যাসাগর স্মরণ শেষ করে ফেলতে চাই।
তবে শুরুতেই বলে রাখি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কোনো নিরেট যুক্তি নয়। হয়ত আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, আর একজনের তার বিপরীত অভিজ্ঞতা আছে। কিংবা, আমি এখানে যা বলতে যাচ্ছি, সেই একই ঘটনায় আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে, যে উপলব্ধির উদ্রেক ঘটেছে, আর কেউ হলে হয়ত ঠিক সেরকম হত না। ফলত, আগে যা বলে এসেছি, তার মধ্যে যুক্তিতর্কই ছিল, কঠোর তথ্য বিশ্লেষণই ছিল, এখন সেদিক থেকে সরে এসে অন্য একটা দিক মেলে ধরতে চাই। বলা যায় না, কারও হয়ত পছন্দও হতে পারে।
মার্ক্সীয় রাজনীতি করার সুবাদে আমাদের মধ্যে {বহুবচনে আপত্তি থাকলে বলব, অন্তত আমার মধ্যে} এরকম একটা ধারণা বেশ সশব্দে প্রচলিত ছিল, বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলন কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল, কেন না, তিনি দেশের বেশির ভাগ জনতাকে সেই সব আন্দোলনে নিজের সঙ্গে পাননি, বা, আরও সঠিক ভাবে বলতে হলে, তিনি তাদের পাওয়ার মতো চেষ্টাও তেমন করে করেননি, তার জন্য অপেক্ষাও করেননি। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজের ভালো কিসে হবে বলে যা বুঝেছেন, একাই তা সম্পাদন করতে এগিয়ে গেছেন। উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ ছিল, কিন্তু উপায় উপযুক্ত ছিল না বলে শেষ অবধি সাফল্য আসেনি। বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন প্রচলিত জীবনী গ্রন্থ এবং বিনয় ঘোষের বিস্তৃত (আদি) মূল্যায়ন পড়ে এই ধারণার পুষ্টি হয়েছিল।
ধারণাটা তারপর একদিন মারাত্মক চোট খেল। কিছু কিছু ক্রমিক ঘটনায়। সমাপ্তির স্বগতোক্তি সেই সব নিয়েই।
১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত আমার বিহার (বর্তমান ঝাড়খণ্ড সহ) থেকে শুরু করে (কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশ বাদে) সারা উত্তর ভারতে ঘোরাঘুরি করার কিঞ্চিত সুযোগ আসে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ (এখনকার ছত্তিসগড় সহ), উত্তর প্রদেশ (বর্তমানের উত্তরাখণ্ড বাদে), হরিয়ানা, পাঞ্জাব—ইত্যাদি রাজ্যের শুধু প্রধান প্রধান শহর নয়, বেশ অনেকটা অভ্যন্তরীন গ্রামাঞ্চলেও যাতায়াত করতে পেরেছিলাম। চলনসই হিন্দি ভাষা শিখে নেওয়ার ফলে নানা ধরনের বহু সংখ্যক মানুষের সঙ্গে আন্তরিক কথা বলার সুবাদে সেই সব অঞ্চলের সমাজ মানস অনেকটা দেখার এবং সম্ভবত বোঝার অনুভূতি লাভ করেছিলাম। তার মধ্যে কয়েকটি ঘটনা এখনও আমাকে মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে স্মৃতি হয়ে স্বপ্নিল চেহারায় এসে জাগিয়ে রাখে। এরকমই দুটি ঘটনার কথা বলতে চাই।
পাঠকদের মনে রাখতে বলব, তখনও বিজেপি আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছয়নি। ধর্ম নিয়ে মুসলমান বিরোধী, জাতপাত নিয়ে দলিত বিরোধী জিগির তুলতে সে শুরু করেছে, কিন্তু গুজরাত দাঙ্গা উত্তর যে মারমুখী ভূমিকায় আজ তাকে দেখা যাচ্ছে, এতটা সহিংস আত্মপরিচয় সে তখনও দিতে পারেনি। তখনকারই ঘটনা এসব।
ঘটনা-এক।
স্থান জয়পুরের মফস্বল। কাল ১৯৮৮-র কোনো এক সময়। পাত্র সতবীর সিং ও অন্যান্য (সকলেরই গল্পিত নাম)।
সতবীরজি পেশায় উকিল। জমাটি মানুষ। আগের বছর আলাপ হয়েছিল। প্রায় বাঙালিদের মতোই হইহই করে আড্ডা দিতে, খেতে এবং খাওয়াতে ভালোবাসেন! জয়পুরে এলে যেখানেই আমার ডেরা পড়ুক, ওনার বাড়িতে কোনো এক দুপুরে এবং কোনো এক রাত্তিরে রাজপুতীয় আহারের নেমন্তন্ন জুটবেই, এবং আগেকার রাজাদের মতোই সেই আদেশ অবশ্য মান্য। কিন্তু এবার জয়পুরে আসা ইস্তক দেখছি, কমরেড কেমন যেন সরে সরে থাকছেন, কথা প্রায় বলছেনই না, দুদিন হয়ে গেছে—আমাকে একবারও বাড়িতে যেতে এবং খেতে বলেননি।
কী ব্যাপার? অন্য কমরেডদের জিগ্যেস করলাম।
তাঁরা খানিকটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর যা বললেন, শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম!
সতবীরজির মেয়ে সরিতা, জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত নিয়ে এম-এ প্রথম বর্ষে পড়ে। ওর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়েরই আইন বিভাগের একটি ছাত্র, হরকিশোরের একটু ইয়ে হয়েছে। বেশ ঘনিষ্ঠতা। অনেকেই জেনে গেছে। সরিতার বাবাও জেনেছেন। তারপর থেকেই তিনি এক অন্য আত্মা। ছেলেটি ‘নীচ’ জাতির। রাজপুতদের ধারে কাছে নয় বংশ মর্যাদায়। জানার কয়েকদিন পরই তিনি মেয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। সে এখন বাড়ির দোতলার কোনো কামরায় সর্বক্ষণ আটক। দরজায় তালা; চাবি সতবীরজির পকেটে। সতবীর সিং এখন দিনরাত বন্দুক নিয়ে ঘুরছেন। হরকিশোরকে নিশানায় পেলেই . . . দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!
শোনা গেল, এই মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর হাসিখুশির দুনিয়ায় ফিরবেন না!
হরকিশোর ফেরারি আসামী।
সব কিছু জানার পরও আমি ওনার সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করেছিলাম। উনি নিরুত্তর এড়িয়ে গেছেন!
না, অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমিও প্রথমে আমার তখন অবধি জানা সাতাশটি হিন্দি সিনেমার কাহিনির কথাই ভেবেছিলাম। ওখানে এরকমই হয়। সামান্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কখনও আবার হরকিশোরদের জাত উঠে যায়, সরিতারা নেমে যায়! তখন বন্দুকের নিশানা থাকে মেয়ের বাবার দিকে। সেরকমের একটা প্লট যে বাস্তবে স্বচক্ষে কোনো দিন দেখতে পাব, সুদূর কল্পনাতেও আগে কখনও আনতে পারিনি।
জয়পুর পার্টি অফিসে বসে আমি এই নিয়ে আমার আক্ষেপের কথা বলছিলাম। নানা কথার এক ফাঁকে জয়পুরের স্থানীয় নেতা সুরেশ চতুর্বেদী বললেন, “কমরেড, হমারে দুর্ভাগ্য ইয়ে হ্যায় কি আপলোগোঁ কে বঙ্গালকে জ্যায়সে হমারে ইহাঁ এক বিদ্যাসাগর উভার কে নহি আয়েঁ। আপ কে ওহাঁ এক বিদ্যাসাগর সে হি সারে অ্যায়সে উলঝাঁ কো সুলঝ দে চুকা।”
বিদ্যাসাগর? আমি অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু উনি তো জাতপাতের বিরুদ্ধে কোনো লড়াই করেননি!
উনি বললেন, না তা করেননি। কিন্তু উনি যেভাবে শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন, হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের গায়ে যে ধাক্কাটা দিয়েছিলেন, শিক্ষিত লোকজনদের যে নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন, তাতেই “শায়দ চুপকে চুপকে” বহু কাজ হয়ে গিয়েছিল। আমরা এখানে সেই জায়গায় এখনও একশ বছর পিছিয়ে আছি!
বিদ্যাসাগরের উপর বিশিষ্ট লেখকদের রচিত বাংলাতে বারো তেরোটা স্বাস্থ্যবান বই পড়েও যে কথাটা কখনও আমার মাথাতে আসতে পায়নি—আমি তো নিশ্চিত, বিদ্যাসাগরের কর্মসূচির ব্যর্থতা বিষয়ে—সেই কথাটা এনারা তাঁর সম্পর্কে শুধু আধা আধা শুনে এবং নিজেদের চারপাশের বাস্তবকে দেখে মিলিয়েই বুঝে ফেলেছেন। গর্ব বোধ করারই তো কথা ছিল, কিন্তু লজ্জায় আমার মাথাটা আপনা থেকেই নীচু হয়ে গেল।
ঘটনা-দুই।
স্থান মোরাদাবাদ। কাল ১৯৯০-এর কোন এক সময়। পাত্র প্রকাশ সিং ও অন্যান্য (এখানেও সব নামই বদলিত)।
প্রকাশ খুব করিতকর্মা ছেলে। ছাত্রফ্রন্টে দারুণ ভালো কাজ করছে। দুটো কলেজে ভালো ভালো যোগাযোগ বের করেছে। ওর আনা কয়েকজন ছাত্র পার্টিতেও যোগ দিয়েছে। এলাকা ওদের নিয়ে জমজমাট হয়ে আছে। বাইরে থেকে আমরা যে যখন মিটিং টিটিং করতে আসি, তাদের আপ্যায়নও সেই অনুযায়ী বেশ একটা তিন-তারা বিশিষ্ট হয় বলে আমার বিশ্বাস (আসলে তারাগুলো কী দিয়ে মাপে আমি জানিই না)। প্রকাশ বিশেষ করে খুব উঁচু গলায় কথা বলে। আমার মিন্মিনে গলার আওয়াজ সে শুনতেই পায় না। মাঝে মাঝেই বলে, “কমরেড অশোকজি, আপ জরা জোর শোর সে বাত কিজিয়েঁ। ইতনি কমজোর বাতোঁ সে ক্রান্তি ক্যায়সে আয়েগি?” ইত্যাদি।
সেবার মোরাদাবাদে গিয়ে দেখি, সেই প্রকাশের গলায় প্রায় আওয়াজ নেই। কথাই বলছে না। খুব মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজটাজ যা করার করছে, কিন্তু কোনো কাজেই যেন উৎসাহ নেই। সুরেশ ত্যাগী ওদের ইন-চার্জ। কমরেড ত্যাগীকেই জিগ্যেস করলাম, কেস্টা কী।
ও যা বলল, শুনে আবারও আমার মাথায় আকাশের বেশ খানিকটা যেন ভেঙে পড়ল।
ওদের গ্রামের ওদের নিজেদের আর অন্য একটা ধরে দুটো পরিবারের মধ্যে বহু দিনের শত্রুতা আছে। রক্তের শত্রুতা। কোনো এক পূর্বপুরুষ থেকে শুরু হয়েছিল, সে আদি কথা ওরাও কেউ এখন আর জানে না। শুধু জানে, ও পক্ষের কেউ এসে এ পক্ষের কাউকে খুন করে গেলে, এদের তরফেও ওদের কাউকে গিয়ে মেরে আসতে হবে।
এরকম একটা দায়িত্ব এবার প্রকাশের কাঁধে এসে পড়েছে। ওদের বাড়ির তরফ থেকে ও বাড়ির একজনকে গিয়ে খুন করে ফেলতে হবে। খুন কে বদ্লে খুন!
থানা পুলিশ হয় না?
না। পুলিশও জানে এসব খুনি-দুশমনির কথা! ওরাও মনে করে, রাজপুত ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এই পারিবারিক ঝগড়া, এ হচ্ছে খানদান কে মামলা। এর মধ্যে ঢোকা মানে দেশের পবিত্র পরম্পরায় হাত দেওয়া। নিজে থেকে ওরা তাই যাবে না। আর যাদের বাড়ির একজন মারা গেল, খুন হল, তারাও পুলিশে অভিযোগ জানাবে না। পুলিশের কাছে যাওয়া মানে তো নিজেকে, পরিবারকে দুর্বল প্রতিপন্ন করা। আমরা নিজেরা বদলা নিতে পারছি না, তাই পুলিশের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করছি। হরগিজ নহি! হমারা সওয়াল, হম খুদ নিপটা লেঙ্গে! গ্যায়র কিসি কো ইস মেঁ ঘুসনা নহি!
প্রকাশ রাজনীতি করতে এসে নিজের চিন্তাধারা বদলে ফেলেছে। ও আর এই পারিবারিক খুনোখুনিতে জড়াতে চায়নি। তাতে বাড়ির লোক, মহল্লার লোকেরা ওকে ‘বুঝদিল’ অর্থাৎ কাপুরুষ বলেছে। শাড়ি-চুড়ি পরে মাথায় এক হাত ঘোমটা টেনে ঘরে পর্দার ভেতরে গিয়ে বসে থাকতে বলেছে। প্রকাশ গ্রামের বাড়িতে না গেলেও এখানে চিঠিপত্র আসছে এই সব বার্তা সহ। সেই থেকেই ও মনমরা হয়ে বসে আছে। যদি এখন এমন কিছু কর্মসূচি নেওয়া যেত যাতে প্রমাণ হয়ে যেত, ও বুঝদিল নয়, লড়তে এবং মরতে জানে, তাহলেই একমাত্র এই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত!
আমি কিছু বলতে পারিনি। কোনো রাস্তা বাতলাতে পারিনি। শুধু সুরেশ ত্যাগীকে বললাম, তোমাদের এখানে এরকম এখনও আছে? এ তো সেই প্রাচীন সামন্তবাদী যুগের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।
ও বলল, “হাঁ তো। আপ কা বঙ্গাল মেঁ রামমোহন বিদ্যাসাগর জ্যায়সে লোগোঁ কে আনে সে, সমাজ শুধার আন্দোলন কি তহত সামন্তবাদ পর কুছ না কুছ চোট পহুঁছি থি। পুরানি বিরাসত কো ছোড় কর লোগোঁ নে মন মেঁ নয়ি নয়ি চিজোঁ কো অপনা লে পায়া। হমারে ইধর অব তক সির্ফ তুলসীদাসজি কে বচন অওর হনুমান চালিশা হি সারে লোগোঁ পর রাজ করতে আয়ে হ্যায়। অ্যায়সে বহোত সারে দিক্কতে ইধর খড়ি হ্যায়!”
আবার সেই ধাক্কা খেলাম বলে অনুভব হল। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর তো আর বেশি কিছু করেননি। দুচারটে সমাজ সংস্কার কর্মসুচি আর আধুনিক শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করে গেছেন। তাতে আর কিছু হয়েছে বলে কখনও মনে হয়নি। এখন এই সব জায়গায় এসে বুঝতে পারছি যে তাঁদের আন্দোলনের আসল সাফল্যের কিছুই আমরা এত কাল ধরে টের পাইনি। বই পড়ে ছবি টাঙিয়ে ভাষণ দিয়ে দৃশ্যমান পরিমাণগত পরিবর্তনেরই শুধু জয়গান গেয়েছি আর তাতেই তৃপ্ত থেকেছি। সমাজের ভেতরে আমাদের দৃশ্যতলের বাইরে যে কখন কিছু কিছু জায়গায় গুণগত পরিবর্তনও ঘটে গেছে, তার তালাশ পাইনি! সেদিন বুঝেছিলাম, বিদ্যাসাগরকে বোঝার এখনও অনেক পথ বাকি থেকে গেছে!
আর তারপরই আরও একটা জিনিস ভেবেছি। ধীরে ধীরে চিন্তাটা মগজে একটা আকৃতি লাভ করেছে।
বিদ্যাসাগরকে আমরা যে বুঝিনি, এর জন্য তাঁরও একটা পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তিনি কোনো স্থায়ী কর্মময় প্রতিষ্ঠান তৈরি করে যাননি। ফলে তিনি নিজেও কোনো প্রতিষ্ঠান হননি। জীবনেও তিনি একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, একক চিন্তাশীল ও কর্মবীর। মরণোত্তর কালেও তিনি একাই। রামমোহন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ। অনেক ত্রুটি দুর্বলতা সীমাবদ্ধতা নিয়েও সেই সংস্থা, তার একাধিক ভগ্নাংশ, দেশে বেশ কিছু কাজের লোক দিয়ে গেছে। সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান সঙ্গীত—জীবনের নানা ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ থেকে দেবব্রত বিশ্বাস। মাঝখানে অসংখ্য। রবীন্দ্রনাথ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান তৈরি করেই নিজেও প্রতিষ্ঠান হয়েছেন। আজও সমাজে জীবনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার ভালো বা মন্দ প্রভাব আছে। ভুল বা ঠিক যেমনই হোক, চর্চা আছে।
ভারতীয় অগ্রসরমান সমাজের পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল হলেও বিবেকানন্দও তাঁর চিন্তা অনুসারী একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে ফেলেছিলেন তাঁর স্বল্পায়ু জীবনেই। সমস্ত ক্ষতিকর প্রভাব নিয়েই সেই প্রতিষ্ঠান—রামকৃষ্ণ মিশন—টিকে গেছে এবং আজও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বেড়ে চলেছে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর নানা ভ্রান্ত দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তা সত্ত্বেও যৌথজীবী আশ্রমের যে সাংগঠনিক ভাবনা নিয়ে এক কালে এগিয়েছিলেন, তা আজ অবধি সারা দেশের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলো গান্ধী আশ্রমের মধ্যে মূর্ত রূপ নিয়ে টিকে আছে। হয়ত ক্ষয়ে যেতে যেতেও আরও অনেক দিনই থাকবে। গান্ধী মরে গেলেও, পৃথিবীর একমাত্র গান্ধীবাদীর মৃত্যু হলেও, রাজনীতির মঞ্চে তাঁর কোনো সত্যকারের অনুগামী আজ না থাকলেও, এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গান্ধীর চিন্তাধারা, গান্ধীবাদ, আরও বহু দিন ভারতের বুকে বেঁচে থাকবে এবং কিছু না কিছু লোককে প্রভাবিত করেই যাবে।
একই ভাবে, বিদ্যাসাগরও যদি তাঁর সমমতাবলম্বী কাছাকাছি থাকা কিছু মানুষকে নিয়ে তাঁর চিন্তাধারায় জ্ঞান অর্জন ও সংস্কৃতি চর্চার সেই ভাবে একটা স্থায়ী কোনো পীঠস্থান তৈরি করে যেতেন—অক্ষয় কুমার দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাধানাথ শিকদার, এমন আরও কেউ কেউ ছিলেন, তাঁদের নিয়ে—তার সম্ভাবনা সেদিন ছিল, নিদেন পক্ষে একটা মতবাদিক পত্রিকারও যদি প্রকাশনা শুরু করতেন, তাহলে হয়ত তাঁর চিন্তাটা সমাজের বুকে স্থায়ী আসন পেয়ে যেত, তিনি যে অবধি করে যেতে পেরেছিলেন, তার পর থেকে বাকি আরদ্ধ কাজ অন্যরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত। মশালটা অনেকের হাতে হাতে ঘুরত। আলোর শিখাটা হয়ত বাড়ত কমত, আলোটা জ্বলতই।
সেই আক্ষেপ তো আছেই।
কিন্তু আরও একটা কথা মাথায় আসছে।
আমরা কি আবার সেই নিবু-নিবু মশালটাকে জ্বালিয়ে দিতে পারি না? একটা যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করে? দেশের চার দিকে তাকিয়ে আজ মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরের সেই আলোকবর্তিকায় আজ আবার গণ সঞ্জীবনের প্রয়োজন।
যারা বুঝবে, দায়িত্ব তাদেরই।
▲
সহায়ক তথ্যসূত্র
১। বিনয় ঘোষ (১৯৭৩), বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (অখণ্ড); ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা;
২। অমল ঘোষ (১৯৭৯), মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর; প্রগ্রেসিভ স্টাডি গ্রুপ, কলকাতা;
৩। বদরুদ্দীন উমর (১৯৮০), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাগালী সমাজ; চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা;
৪। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০১১), বিদ্যাসাগর: নানা প্রসঙ্গ; চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা;
৫। গোপাল হালদার (সং ১৯৭২), বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, তিন খণ্ড; বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, কলকাতা;
৬। ফেসবুকের (সহমত-বিপ্রমত) বন্ধুদের পোস্ট ও মন্তব্য সমূহ।
[সমাপ্ত]
লেখক পরিচিতি: ‘সেস্টাস’ নামে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক। বিজ্ঞান ও মার্কসবাদের আলোয় বিজ্ঞানের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে লোকপ্রিয় প্রবন্ধের লেখক।


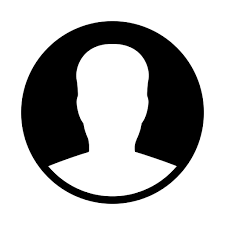
ভাবনার অনেক অনেক জানালা খুললো বুঝি। আপনার বিদ্যাসাগর চিন্তা আমার মতো অনেককেই নাড়া দিয়েছে নিশ্চিত, এটুকু আশা করা যেতেই পারে। আপনার পরবর্তী কাজের দিকে তাকিয়ে রইলাম।